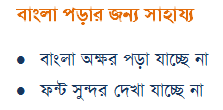ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের যুগে মানবতার আত্মিক বিপর্যয়
প্রাচ্যের এশীয় জাতি ও জনগোষ্ঠীগুলোর জাগতিক ও বস্ত্তগত দুর্গতি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য কীভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, কীভাবে তাদের সুবিপুল সম্পদ-সম্ভার লুণ্ঠিত হয়েছে এবং কীভাবে দেশের পর দেশ ও জনগোষ্ঠীর পর জনগোষ্ঠী পাশ্চাত্যের জাগতিক শক্তি ও রাজনৈতিক ধূর্ততার কাছে পরাজিত হয়েছে, সে বড় দীর্ঘ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস, যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু লেখক-ঐতিহাসিক এ বিষয়ে কলম ধরেছেন এবং বিভিন্ন মানের, বিভিন্ন কলেবরের বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে যেহেতু আমাদের মূল আলোচ্যবিষয় হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বের পতন এবং তার অনিবার্য ফলরূপে ইউরোপীয়দের আধিপত্য বিস্তারের কারণে বিশ্বের কী ক্ষতি হয়েছে তা তুলে ধরা, সেহেতু এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে ও সঙ্কেতে তুলে ধরতে চাই যে, ইউরোপের এই সর্বগ্রাসী আগ্রাসন, যার ভয়াবহ প্রভাব থেকে পর্বতের চূড়া ও গভীর উপত্যকা, ভৌগলিক পরিবেশ ও দেশের জলবায়ু, এমনকি স্বাধীন জনগোষ্ঠীগুলোর বিবেক-বুদ্ধিও নিরাপদ থাকেনি, এরূপ ভয়াবহ আগ্রাসনের মুখে মানবজাতি ও মানবসভ্যতা হৃদয় ও আত্মা, নীতি ও চরিত্র এবং চিন্তা ও বিশ্বাসের
ক্ষেত্রে কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ এ শোকের, এ বিপর্যয়ের সত্যি কোন সান্তবনা ও ক্ষতিপূরণ নেই। এমনকি খুব অল্প মানুষই এর ব্যাপকতা ও গভীরতা বুঝতে পেরেছেন। আর সেই অল্পেরও খুব অল্পসংখ্যক এ বিষয়ে কলম ধরেছেন।
বিজিত জনপদ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেহেতু একমাত্র মুসলিম উম্মাহই ছিলো স্বতন্ত্র বোধ, বিশ্বাস,
সংস্কৃতি, নীতি ও চরিত্রের অধিকারী এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থাই ছিলো জাহেলিয়াতের আসল প্রতিদ্বন্দ্বী সেহেতু খুব স্বাভাবিক কারণেই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শাসন-শোষণে মুসলিম উম্মাহর ক্ষতি ও বিপর্যয়ই ছিলো সবচে’ বেশী। এবং তাদেরই উপর দিয়ে বয়ে গেছে ঝড়-তুফানের আসল প্রলয়তা-ব।
বস্ত্তত স্বভাব ও প্রকৃতিতেই ইসলাম ও জাহেলিয়াত হচ্ছে ‘তারাজু’র দুই পাল্লা। সুতরাং একটি পাল্লা নীচে নামলে অন্যটি অনিবার্যভাবেই উপরে উঠে যাবে। মধ্যযুগে তাতারী হামলার ক্ষেত্রে যেমন এটা হয়েছে, আধুনিক যুগে ইউরোপীয় আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও এটাই হয়েছে। তো ইউরোপীয় জাহেলিয়াতের আগ্রাসনের মুখে মুসলিম উম্মাহ কোন্ কোন্ আত্মিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো, এখানে একে একে সেগুলো আমরা আলোচনা করছি।
ধর্মীয় অনুভূতির বিলুপ্তি
এই যে জগত-সংসার, এই যে জীবন ও তার দৌড়ঝাঁপ, এর শেষ পরিণতি কী? মানুষ কোত্থেকে এসেছে, কোথায় যাবে? মৃত্যুর পর অন্যকোন জীবন কি আছে? যদি থাকে, কেমন সে জীবন? কী তার রূপ ও প্রকৃতি? দুনিয়ার এই দু’দিনের জীবনে কি সেই অনন্ত জীবনের জন্য কোন হিদায়াত ও বিধান-ব্যবস্থা রয়েছে? যদি থাকে, কোন উৎস থেকে মানুষ তা অর্জন করতে পারে এবং কার তারবিয়াত ও তত্ত্বাবধানে তা নির্ভুলভাবে পালন করতে পারে? আখেরাতের সফল জীবন এবং অনন্ত সুখ-শান্তি ও চিরসৌভাগ্য অর্জনের পথ ও পন্থা কী এবং তা কে বলে দেবে?
প্রাচ্যের জীবন ও চিন্তায় এগুলো ছিলো এমন জ্বলন্ত প্রশ্ন যা মানুষকে যুগযুগ ধরে অস্থির ও ব্যাকুল করে রেখেছিলো; এমনকি চরম ভোগবাদিতা ও আত্মবিস্মৃতির যুগেও হৃদয় ও আত্মার এই সব অস্থির জিজ্ঞাসা সম্পর্কে সে উদাসীন থাকতে পারেনি। তার অন্তরাত্মা বারবার তাকে এভাবে জিজ্ঞাসা করেছে এবং জবাব
চেয়েছে। প্রাচ্যের মানুষ তার সুদীর্ঘ জীবন-ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে
হৃদয় ও আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত এসকল জিজ্ঞাসাকে উপেক্ষা করতে পারেনি; পারেনি জীবন-সংসারের জটিলতার অজুহাতে ভিতরের আওয়ায শুনেও না শোনার ভান করে থাকতে, বরং সে কান পেতে শুনেছে, নিবিষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে এবং জাগ্রত মস্তিষ্কে চিন্তা করেছে; কে আমি? কোত্থেকে এসেছি? কোথায় যাবো? কীভাবে এ জীবনে ঐ জীবনের প্রস্ত্ততি গ্রহণ করবো? জীবনের অব্যাহত ব্যস্ততা ও ত্রস্ততা এবং বুদ্ধিবৃত্তির নিরন্তর প্রয়াস-সাধনার মধ্যে এ প্রশ্নগুলোকেই সে অগ্রাধিকার দিয়েছে। জ্ঞান ও সভ্যতার বহু সহস্রবৎসরব্যাপী ইতিহাসে এ সকল জিজ্ঞাসার উত্তরসন্ধানেই সে ব্যাপৃত ছিলো। কখনো যুক্তিতে, কখনো ভক্তিতে; কখনো বিতর্কে, কখনো বিশ্বাসে কিছু সে গ্রহণ করেছে, আবার কিছু বর্জন করেছে। কখনো সত্য থেকে সরে গেছে, কখনো সত্যের কাছে এসেছে। কখনো তার সামনে আলো ছিলো, কখনো ছিলো আঁধার, কিন্তু তার সত্যসন্ধানের অভিযাত্রা কখনো থেমে থাকেনি। প্রাচ্যের গর্বের সম্পদরূপে স্বীকৃত এই যে বিভিন্ন দর্শন ও আত্মদর্শন, দেহতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক সাধনা ও নির্বাণপ্রয়াস এবং বিভিন্ন ঊর্ধ্বজাগতিক চর্চা-অনুশীলন ও পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ, এগুলো আর কিছু নয়, মানুষের স্বভাবজাত ঐসব প্রশ্নের উত্তরসন্ধানের বিভিন্ন প্রয়াস মাত্র। এ সুদীর্ঘ প্রয়াস-প্রচেষ্টায় মানুষ সফল হয়েছে, না ব্যর্থ, তা মুল বিষয় নয়; মূল বিষয় হলো, প্রাচ্যের জীবনে এসকল প্রশ্ন সর্বদা জাগরূক ছিলো এবং উত্তরসন্ধানের প্রাণান্ত প্রয়াস অব্যাহত ছিলো। পথ দীর্ঘ, দুর্গম ও অন্ধকার ছিলো; গন্তব্য ছিলো অচেনা, অজানা ও রহস্যঘেরা, কিন্তু তার পথ চলা এবং একের পর এক অভিযাত্রা অব্যাহত ছিলো; যা প্রমাণ করে যে, প্রাচ্যের জীবনে এটি ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং তার কৌতূহল, ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা ছিলো সীমাহীন।
এক্ষেত্রে দার্শনিক পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায়, প্রাচ্যের মানুষ ‘পঞ্চ-ইন্দ্রিয়’র পাশাপাশি ষষ্ঠ একটি ইন্দ্রীয়‘র অধিকারী ছিলো, যাকে আমরা ‘ধর্মেন্দ্রিয়’ বলতে পারি।
তো প্রতিটি ইন্দ্রিয় যেমন নিজস্ব ক্ষেত্রে কাজ করে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য আহরণ করে, তেমনি এই ‘ধর্মেন্দ্রিয়’রও রয়েছে নিজস্ব কিছু অনুভবযোগ্য বিষয়, যা প্রাচ্যের
চিন্তা-জীবনের অপরিহার্য অংশ।
এটা অবশ্য ঠিক যে, নবজাগর- ণের প্রথম দিকে ইউরোপেও এ সকল প্রশ্ন জাগরূক ছিলো এবং চিন্তাশীল ও বিদ্বানসমাজ এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত ছিলো। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জীবনদর্শনের অন্তর্গত গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো যতই সামনে এসেছে এবং ভোগবাদ ও বস্ত্তবাদের বেড়াজালে তারা যতই জড়িয়ে পড়েছে, হৃদয় ও আত্মার জিজ্ঞাসার গুরুত্ব ততই কমে এসেছে এবং বাস্তব জীবনে ততই তা ভোগ ও চাহিদার নীচে চাপা পড়ে গেছে। অতিপ্রাকৃতিক দর্শনের পরিমন্ডলে হয়ত এখনো এসব প্রশ্নের তাত্ত্বিক আলোচনা হয়, কিন্তু জীবন থেকে তা এমনভাবে নির্বাসিত হয়েছে যে, প্রশ্নবোধক চিহ্নটিও মুছে গেছে। আত্মজিজ্ঞাসার যে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা এবং যে অন্বেষা ও অনুসন্ধিৎসা প্রাচ্যকে শত-সহস্র বছর অস্থির করে রেখেছিলো পাশ্চাত্যের জীবনে তা ছিলো সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। আর অবশ্যই তা এজন্য নয় যে, এক্ষেত্রে তারা বিশ্বাস ও প্রত্যয় এবং স্বস্তি ও আশ্বস্তি লাভ করেছে, বরং এ জন্য যে, জীবনে এর গুরুত্বই শেষ হয়ে গেছে এবং অন্যবহু ব্যস্ততা, সমস্যা ও জটিলতা এর স্থান দখল করে নিয়েছে। আজকের সদাব্যস্ত ও ভোগসর্বস্ব মানুষ হৃদয় ও আত্মার জিজ্ঞাসার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, নিস্পৃহ ও রহিতসম্পর্ক। এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা ও উত্তর অন্বেষণের কোন অবকাশই তাদের জীবনে আর নেই। কারণ তাদের কাছে জীবন মানেই হলো যা দেখা যায় এবং নগদ ভোগ করা যায়। এখন তাদের একমাত্র কাম্য হলো, ভোগের চাহিদা বৃদ্ধি করার এবং আরো আনন্দঘনরূপে তা চরিতার্থ করার বিশদ দিকনির্দেশনা।
প্রাচীন প্রাচ্য এবং আধুনিক পাশ্চাত্যের মধ্যে এ এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য যে, প্রাচ্য ‘ধর্মেন্দ্রিয়’ নামে একটি অন্তর্শক্তির অধিকারী ছিলো, পক্ষান্তরে সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। আর কোন ইন্দ্রিয় শক্তি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন সংশ্লিষ্ট অনুভবও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্ধের কাছে তাই অর্থহীন দৃশ্যজগত ও তার বর্ণবৈচিত্র্য; আর বধির জানে না শব্দ-জগতের খবর। তদ্রূপ ধর্মেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত যে, তার কাছে এর দ্বারা অনুভবযোগ্য সকল বিষয় অস্তিত্বহীন। গায়বের সকল সত্য তার কাছে অলীক কল্পনা মাত্র। আখেরাত, জান্নাত- জাহান্নাম, আযাব ও ছাওয়াব, আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, তাকওয়া ও পবিত্রতা, এগুলো তার কাছে অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। এমন কোন ডাক ও আহবানের প্রতি তার কোন অনুরাগ-আকর্ষণ নেই যার সম্পর্ক পঞ্চেন্দ্রিয়ের সঙ্গে নয়, যা নগদ ভোগ-আনন্দের কথা বলে না। অন্তরকে ঝাঁকুনি দেয়, হৃদয়কে বিগলিত করে এবং চোখকে অশ্রুসিক্ত করে, এমন কোন ঘটনা, বাণী ও উপদেশ তার মধ্যে কোন রেখাপাতই করে না।
ধর্মেন্দ্রিয়-বঞ্চিত এসমস্ত লোকদের পক্ষ হতেই যুগে যুগে আম্বিয়া ও ওয়ারিছীনে আম্বিয়া সবচে’ কঠিন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন। কোন উপদেশ ও ধর্মকথা এবং কোন দরদ-ব্যথা ও অশ্রুপাত তাদের মধ্যে সামান্য প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করতে পারেনি। তাদের হৃদয়ের তাপ ও উত্তাপ এমন শীতল হয়ে গিয়েছিলো যে, তাতে সামান্য উষ্ণতা সৃষ্টিরও আর অবকাশ ছিলো না। তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিলো যে, ধর্মের কথায় তারা কান দেবে না এবং ধর্মের কোন আবেদনে আর সাড়া দেবে না। পাথর গলে মোম হয়ে যায়, এমন দাওয়াত শুনেও যুগে যুগে এরাই বলে উঠতো, ‘আমাদের ইহ জীবন ছাড়া তো আর কিছু নেই। (এখানে) আমরা বাঁচবো এবং মৃত্যুবরণ করবো। আর মৃত্যুর পর আমরা কিছুতেই পুনর্জীবিত হবো না।’
নবী ও পয়গম্বর যখন তাদেরকে তাদেরই ভাষায় সহজ-সরল কথায় উপদেশ দিতেন এবং দ্বীনের পথে দাওয়াত দিতেন তখন তারা ‘আপসে আপ’ বলে বসতো, ‘তুমি যা বলো তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না, আর তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে দুর্বল।’
পাশ্চাত্য সভ্যতার এই চরমোৎক- র্ষের যুগে সকল জনপদেই বিরাট একটা শ্রেণী এমন রয়েছে যাদের অতিব্যস্ত ও ভোগসর্বস্ব জীবনে ধর্মের নামে কোন স্থানই বরাদ্দ নেই। দুনিয়ার লোভ-লালসা ও মোহগ্রস্ততা তাদের এমন সীমাহীন যে, বহু সাধ্য-সাধনার পরো একজন দা‘ঈ ও আহবানকারী এমন কোন ছিদ্রপথও খুঁজে পান না যাতে তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্কে দ্বীন, ঈমান ও আখলাকের দাওয়াত প্রবেশ করতে পারে। কেউ যদি সুরের ‘সারগম’ না জানে, কিংবা স্বভাব ও প্রকৃতির কাছ থেকে কাব্যরুচি ও ছন্দবোধ না পেয়ে থাকে, তার জন্য যেমন সেরা সঙ্গীত ও শ্রেষ্ঠ কবিতাও অর্থহীন, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ধর্মেন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত তার মধ্যে নবীর দাওয়াত ও উপদেশ, আসমানি কিতাবের হিদায়াত ও পথনির্দেশ এবং আলিমের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও বক্তব্য, এসবই নিছক অরণ্যে রোদন এবং নিভে যাওয়া ছাইভষ্মে ফুঁক দেয়া বলে প্রমাণিত হয়। আরব জাহেলিয়াতের কবি সেই কবে বলে গেছেন- ‘জীবজন্তুকে আওয়াজ দিলে শুনতো, কিন্তু তুমি ডাকছো যাকে, তার দেহে তো প্রাণ নেই।’
এমন লোকদের সম্বোধন করার, উপদেশ দেয়ার এবং দ্বীন ও আখলাকের দাওয়াত পেশ করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে তারা নীচের কোরআনি আয়াতগুলোর মর্ম ও রহস্য ভালো বোঝবেন-
‘মোহর করে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের কলবে এবং তাদের কানে, আর তাদের চোখে রয়েছে পর্দা।’
‘নাকি আপনি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে বা বোঝে। তারা তো পশুর মত, বরং পশুর চেয়েও ভ্রষ্ট।’
‘আর যারা কুফুরি করে তাদের উদাহরণ হলো ঐ লোকের মত যে, চিৎকার করছে এমন কিছুর পিছনে যা হাঁক-ডাক ছাড়া কিছু শুনতে পায় না। এরা বধির, বোবা ও অন্ধ।’
বস্ত্তত দাওয়াতের বাস্তব অভিজ্ঞতা এ জাতীয় আয়াত সম্পর্কে ঐসব প্রশ্ন ও দ্বিধা-সংশয় অন্তর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে দেয়, যা নিছক তাত্ত্বিক তাফসীরের ক্ষেত্রে দেখা দেয়।
বর্তমান যুগের আসল ব্যাধি, যা ঔষধে ধরে না এবং চিকিৎসায় সারে না, তা হচ্ছে দ্বীন, ঈমান, কালব ও রূহের বিষয়ে চরম উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা। বস্ত্তত, অনাচার ও পাপাচারের ঘোর অন্ধকার যুগেও এবং চরম বিরোধিতার কঠিন গোলযোগের সময়েও দ্বীনী দাওয়াত ও ইছলাহি মেহনত অতটা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়নি যতটা হচ্ছে দ্বীন ও আখলাক এবং রূহ ও রূহানিয়াতের প্রতি চরম নির্লিপ্ততার এ ‘শান্তিপূর্ণ’ যুগে। বে-তলব ও নির্লিপ্ত মানুষের তো কিছুতেই কিছু যায় আসে না। পানির পিপাসাই যার নেই তাকে কূপের সন্ধান বলে কী লাভ! কোরআনের ভাষায়-
‘তুমি তো ডাক শোনাতে পারবে না মৃতদের এবং শোনাতে পারবে না বাধিরদের, যখন তারা পিঠ দেখিয়ে চলে যায়।’
পাশ্চাত্যের বড় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে- র দর্শন ও মনস্তত্ত্ব বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক প্রাচীন ও আধুনিক মনমানসের এই বুনিয়াদি পার্থক্য ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছেন এবং সুসংক্ষিপ্ত ভাষায় তা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ‘আগে ধর্মবিষয়ে প্রশ্ন-সংশয় দেখা দিতো, যার হয়ত সমেত্মাষজনক উত্তর থাকতো না, কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের ধাত এই যে, কোন প্রশ্ন তাদের নাড়াই দেয় না।’
দ্বীনী আবেগ-অনুভূতির বিলুপ্তি-
পর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি যে, ইসলামী শাসন ও সভ্যতার সোনালী যুগে পৃথিবীর অবস্থা কী ছিলো এবং মুসলিম উম্মাহ তখন কী কী গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো? এককথায়, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, সর্বক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর জীবন ছিলো দ্বীনমুখী ও আল্লাহ-অভিমুখী। মানুষের মধ্যে দ্বীনের তলব-তালাশ ও ধর্মীয় প্রেরণা-উদ্দীপনা ছিলো ব্যাপক। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ সত্য এই যে, যে কোন উত্থানের জন্যই রয়েছে পতন, আর জীবনের সর্বক্ষেত্রে পতনের উপকরণগুলো সবার অলক্ষ্যেই যেন দানা বাঁধতে শুরু করে এবং একসময় শিকড় এত গভীরে চলে যায় যে, তা নির্মূল করা এবং জীবনের গতিকে সঠিক খাতে ফিরিয়ে আনা আর সম্ভব হয় না। ইতিহাসের এই অমোঘ বিধান থেকে মুসলিম উম্মাহও মুক্ত ছিলো না। পতনের ধারা সেখানেও শুরু হয়ে গেলো এবং অধঃপতনের সকল উপকরণ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু ওলাময়ে উম্মত, যাদের দায়িত্বই হলো উম্মাহর দ্বীনী তত্ত্বাবধান, আল্লাহ তাঁদের দান করেছেন পর্বতের অবিচলতা এবং সিংহের সাহস, উম্মাহর পতন ও অধঃপতনের যুগেও তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে গেলেন। শেষ যুগে যখন ভোগবাদ ও বস্ত্তবাদের সাগর-জোয়ারে মুসলিম বিশ্ব ভেসে গেলো তখন ওলামায়ে উম্মত সেই ঝড়বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ছোট ছোট দ্বীপ-উপদ্বীপ তৈরী করে নিলেন, দ্বীন ও দ্বীনের অনুসারীরা যেখানে আশ্রয় নিতে এবং ঈমান ও বিশ্বাসের শেষ সম্বলটুকু রক্ষা করতে পারে। দ্বীনের ধারক, বাহক ও রক্ষক এই মহান ব্যক্তিগণ যেন অন্ধকার সমুদ্রে আলোর মিনার ছিলেন। মানুষকে তারা জড়বাদ ও বস্ত্তবাদের ঘূর্ণাবর্ত থেকে উদ্ধার করে আনতেন এবং দ্বীনী তারবিয়াত ও আধ্যাত্মিক সংশোধন দ্বারা তাদের ঝড়- তুফানের মুকাবেলা করে জীবনের লক্ষ এগিয়ে চলার যোগ্যরূপে গড়ে তুলতেন। পরবর্তী যুগে তারাই ছূফিয়া ও মাশায়েখ নামে অভিহিত হয়েছেন।
বলা যায়, শেষ শতাব্দীগুলোতে এই মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণই ছিলেন মুসলিম সমাজের ধার্মিকতা ও ধর্মানুরাগ পরিমাপের মোটামুটি মানদ-। অর্থাৎ তাঁদের প্রতি সাধারণ মুসলিমের ভক্তি-মুহববতের গভীরতা থেকেই আমরা ধারণা করতে পারি যে, তখন মানুষ বস্ত্তবাদিতা ও দুনিয়ামুখিতা হতে কতটা দূরে ছিলো এবং তাদের অন্তরে দ্বীনের তলব ও তড়প কেমন ছিলো।
মুসলিম বিশ্বের সকল কেন্দ্রীয় শহর ও জনপদে এমন নূরানী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিলো যারা ভোগবাদিতা ও বস্ত্তবাদিতার ‘অন্ধকার সমুদ্রে’ সত্যি সত্যি ছিলেন আলোর মিনার। সেই আধ্যাত্মিক আলোর আকর্ষণে চারদিক থেকে মানুষ পতঙ্গের মত এসে ঝাঁপিয়ে পড়তো। দুনিয়ার দূরদারায ও দূর-সুদূর এলাকা থেকে বিভিন্ন ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ তাদের খানকায় জড়ো হতো। বলা যায়, সেগুলো ছিলো মুসলিম উম্মাহর আন্তর্জাতিক বসতি, যেখানে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ, সকল এলাকার সকল গোত্রের মুসলমানদের দেখা পাওয়া যেতো। আজকের পরিভাষায় বলা যায়, সুবিসত্মৃত ইসলামি জাহান যেন নিজেকে গুটিয়ে এখানে মেলে ধরেছিলো।
আমাদের এ উপমহাদেশ ইসলামি জাহানের এক প্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু এ ভূখন্ড সবসময় ছিলো দ্বীনী তলব ও ধর্মীয় চেতনা এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে প্রত্যেক যুগে মুসলিম শাসকদের রাজত্যের পাশাপাশি রূহানিয়াতেরও বহু স্বাধীন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিলো, যেখানে হাজার হাজার মানুষ সমকালের বস্ত্তগত লোভ-লালসা ও প্ররোচনা উপেক্ষা করে এবং রাজা ও রাজনীতির উত্থান-পতন থেকে নির্লিপ্ত হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও রূহানি তরক্কির সাধনা ও মুজাহাদায় নিমগ্ন থাকতেন।
হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর আধ্যাত্মিক কেন্দ্র ও রূহানি মারকায গিয়াছপুর হচ্ছে এর উত্তম উদাহরণ, যা মুসলিম ভারতের শাসনকেন্দ্র স্বয়ং দিলস্নীতে অবস্থিত ছিলো। এই স্বাধীন আধ্যাত্মিক কেন্দ্র (গিয়াছুদ্দীন বলবন থেকে গিয়াছুদ্দীন তুগলক পর্যন্ত) একে একে আটজন প্রতাপশালী মুসলিম শাসকের শাসনকাল প্রত্যক্ষ করেছে এবং প্রায় সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দিকাল নিজের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও নির্মুখাপেক্ষিতা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছিলো। ইরানের ‘সন্জর’ থেকে পূর্বভারতের ‘ঔধ’ পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের আধ্যাত্মিকতা ও রূহানিয়াতের পিপাসু মানুষ দলে দলে এখানে এসে পড়ে থাকতো। যদি তরীকতের সমস্ত সিলসিলার ছুফিয়া-মাশায়েখের খানকাহগুলোর আবাদি এবং জনসমাগমের বিশদ বিবরণ লেখা হয় (যা দ্বারা সে যুগের মানুষের ধর্মপ্রেম, আল্লাহমুখিতা ও দ্বীনী তলবের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়) তাহলে এ সংক্ষিপ্ত কলেবরে তার সঙ্কুলান হবে না। তাই নমুনাস্বরূপ শুধু একটি সিলসিলার কয়েকজন বুযুর্গানের সঙ্গে সমকালের সাধারণ মানুষের ভক্তি-মুহববতের সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি। তাতে কিছুটা হলেও অনুমান করা যাবে যে, তাঁদের যুগে, যা ছিলো ভোগবাদিতা ও দুনিয়ামুখিতার চরম যুগ, তখনো মানুষের ধর্মপ্রেম ও আল্লাহমুখিতার কী বিস্ময়কর অবস্থা ছিলো এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার পিপাসা মানুষকে কাহাঁ কাহাঁ মুলুক থেকে চুম্বক-আকর্ষণের মত এখানে টেনে আনতো।
শায়খ আহমদ সারহিন্দী, মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ, মৃ. ১০৩৪ হিঃ)-এর ‘সম্পর্কী’ যারা তাদের তালিকা দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন, হিন্দ-আফগানিস্তানের কত শহর-জনপদের কত বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং জাহাঙ্গীর-যুগের কত বড় বড় আমীর-উমরা ও রাজপুরুষ তাঁর বাইআতের সিলসিলায় দাখিল ছিলো এবং কত দূরদারায এলাকা থেকে মানুষ তাঁর রূহানি ফায়য ও ফায়যান হাছিল করার জন্য আসতো।
তাঁর বিশিষ্ট খলিফা হযরত সাইয়েদ আদম বিন্নূরী (রহ. মৃ ১০৫৩ হিঃ)-এর খানকার দস্তরখানে দৈনিক মেহমান ছিলো একহাজার। শত-সহস্র ভক্ত-অনুরাগী আলিম-ওলামা ছিলেন তাঁর সওয়ারির অনুগামী। ‘তাযকিরায়ে আদমিয়া’ কিতাবে আছে, ১০৫২ হিজরীতে, মৃত্যুর এক বছর আগে তিনি লাহোরে তশরীফ আনেন। তখন ‘সাদাত’, ওলামা-মাশায়েখ ও অন্যান্য শ্রেণীর দশহাজার মানুষ তাঁর সফরসঙ্গী ছিলো। তালিবীন ও শিষ্যদের এত বড় মজমা তাঁকে ঘিরে থাকতো যে, শাহজাহানের মত সম্রাটও শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাঁর খিদমতে এই পায়গামসহ কিছু আশরাফী হাদিয়া পাঠান যে, এখন তো আপনার উপর হজ্ব ফরয হয়ে গেলো। সুতরাং আপনি হারামাইন শরীফাইনের ‘ইচ্ছে’ করুন।
শায়খ সম্রাটের ‘ইশারা’ বুঝলেন। দুনিয়ার হুকুমত ও শাহানশাহির লোভ তো তাঁর ছিলোই না। তিনি তখনি হিজরত করলেন এবং হারামাইনে তাঁর ইনতিকাল হলো।
হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানি (রহ.)-এর সুযোগ্য পুত্র ও খলীফা হযরত খাজা মা‘ছূম বিল্লাহ (মৃত, ১০৭৯ হি.)-এর হাতে নয় লাখ মানুষ তাওবাকরত বাই‘আত হয়েছেন এবং সাত হাজার ব্যক্তি খিলাফাতের সনদ-সৌভাগ্য লাভ করেছেন।
তাঁর ছাহেবযাদা শায়খ সাইফুদ্দীন সারহিন্দি (রহ. মৃত, ১০৯৬ হি.)-এর দিলস্নীর খানকায় ‘তালিবীনসমাগম’ কেমন ছিলো, তা কিছুটা অনুমান করা যায় ‘যায়লুর-রাশাহাত’ কিতাবের এই তথ্য থেকে যে, একহাজার চারশ মানুষ দু’বেলা তাঁর দস্তরখানে শরীক হতো, আর খাবার তৈরী হতো মেহমানদের পছন্দ ও ফরমায়েশ অনুযায়ী।
আওলিয়া-মাশায়েখদের সঙ্গে সমাজের বিত্তশালী ও অভিজাত শ্রেণী এবং আমীর-ওমরাদের যে গভীর সম্পর্ক ছিলো এবং যার ভিত্তি ছিলো শুধু দ্বীনী মুহববত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা, তার একটি নমুনা দেখুন। হযরত খাজা মুহম্মদ সারহিন্দী যখন বাসস্থান থেকে মসজিদে গমন করতেন তখন তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শাল ও রুমাল বিছিয়ে দিতেন, যেন কদম মাটিতে না পড়ে। রোগীর তত্ত্ব নিতে, বা অন্য কোন প্রয়োজনে কোথাও গেলে তাঁর সওয়ারি বের হতো শাহী শান ও জালালের সঙ্গে। আমীর-ওমরাদের পাল্কী ও সওয়ারি হতো তাঁর অনুগামী ।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-যুগে ধীরে ধীরে যখন মুসলিম হুকুমতের তখতা উল্টে গেলো, তার কিছুকাল আগ পর্যন্তও মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে এই দ্বীনী তলব ও যওক-শওক এবং ধর্মানুরাগ ও আল্লাহমুখিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। হযরত মিরযা মাযহার জানেজানাঁ রহ.-এর খলিফা হযরত শাহ গোলাম আলী রহ. (মৃত ১২৪০ হি.)-এর যুগে দিলস্নীর মুজাদ্দিদী খানকাহ ছিলো তালিবীনের বিরাট সমাগমকেন্দ্র। ‘আছারুছ্-ছানাদীদ’ কিতাবে স্যার সইয়দ আহমদ খান লিখেছেন-
‘হযরতের খানকাহে আমি নিজের চোখে দেখেছি, রোম, শাম, বাগদাদ, মিসর, চীন ও হাবাশা থেকে আগত লোকেরা বাই‘আত হচ্ছেন এবং পরম সৌভাগ্য মনে করে খানকাহের খিদমত করছেন। আর নিকটবর্তী জনপদ, হিন্দুস্তান, পানজাব ও আফগানিস্তানের কথা তো বলাই বাহুল্য। যেন পতঙ্গদল ছেয়ে থাকতো। খানকাহের নিয়মিত বাসিন্দা, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে আসতেন তাদের সংখ্যা পাঁচশর কম কখনো হতো না। তাদের সবার রুটি-কাপড় ছিলো হযরতের যিম্মায়।’
২৮শে জুমাদাল উলা ১২৩১ হি., শুধু এই একটি তারিখে তাঁর ফায়য হাছিল করার জন্য যত শহর- জনপদ থেকে তালিবীনের সমাগম হয়েছিলো তার তালিকা দেখুন-
‘সমরকন্দ, বোখারা, গযনি, তাশকন্দ, হিছার, কান্দাহার, কাবুল, পেশোয়ার, কাশ্মীর, মুলতান, লাহোর, সিন্ধু, আমরোহ, সম্ভল, রামপুর, বেরেলী, লৌখনো, ঝাসি, বাহরাইচ, গোরখাপুর, আযীমাবাদ, ঢাকা, হায়দারাবাদ, পুনা, ইত্যাদি।’
এটা তখনকার কথা যখন আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিলো না। পদব্রজই ছিলো প্রায় একমাত্র উপায়।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগে ইংরেজ রাজত্ব পাকা-পোক্ত হওয়ার কিছু আগে হযরত সইয়দ আহমদ শহীদ ও তাঁর ‘জাঁনেছার’ মুবালিস্নগগণ দিকভ্রান্ত মুসলিম মিল্লাতকে ‘ডাক’ দিয়েছিলেন এবং ‘ধাবিত হও আল্লাহর দিকে’-এ আওয়ায বুলন্দ করেছিলেন। বস্ত্তত সেটা ছিলো মুসলিম সমাজে শিকড় গেড়ে বসা গাফলাত, নাফরমানি ও শরিয়ত-বিমুখ জীবনাচারের বিরুদ্ধে আপোসহীন জিহাদ ও মুজাহাদার সূচনা। মুসলিমগণ তখন যে আবেগ-উদ্দীপনা ও জোশ-জাযবার সঙ্গে লাববাইক বলে সাড়া দিয়েছিলো, যেমন পতঙ্গের মত তাঁর কাফেলায় ছুটে এসেছিলো, প্রত্যেক জনপদে তাঁর প্রেরিতদের যে ত্যাগ ও বদান্যতা, যে ভক্তি ও বিনয়নম্রতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলো, গুলিস্তানে হিন্দের সেরা ফুলগুলো যেভাবে তাঁর গলার হার হয়েছিলো, তারপর বালাকোটে ধূলিলুণ্ঠিত হয়েছিলো, তা থেকে সহজেই বোঝা যায়, সেই অধঃপতনের যুগেও মুসলিম সমাজে কী সাহস ও মনোবল ছিলো, কী বিপুল উদ্যম ও কর্মশক্তি ছিলো, কী জোশে জিহাদ ও শওকে শাহাদাত ছিলো এবং আত্মসংশোধন ও মুজাহাদার কী তলব ও তড়প ছিলো!
তখনকার মুসলিমদের দ্বীনী হালাত সম্পর্কে আরো কিছু ধারণা পেতে হলে আপনি ঐসমস্ত দাওয়াতি সফরের বিবরণ পড়ুন, যা সৈয়দ ছাহিব প্রথমে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চলের শহর-জনপদে এবং পরে অযোধ্যায় করেছেন। আরো স্পষ্ট ও জীবন্ত ধারণা আপনি পাবেন সৈয়দ ছাহিবের ১২৩৬ হিজরীর হজ্ব-সফরের রোয়েদাদ থেকে। এই দীর্ঘ সফরে তিনি পূর্বভারতের ঐ বিশাল এলাকা অতিক্রম করেছেন যা এখন যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বাংলা, এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত। সাড়ে সাতশ মানুষের বিরাট কাফেলা সৈয়দ ছাহেবের জন্মভূমি রায়বেরেলী থেকে রওয়ানা হয়ে কলকাতায় গিয়ে পানির জাহাযে উঠেছিলো। কাফেলার পুরো যাত্রাপথে ছিলো অভূতপূর্ব সাজসাজ ও আলোড়ন। সর্বত্র একই ‘মানযার’, একই দৃশ্য; দ্বীনের তলবে বে-কারার মানুষ পতঙ্গের মত ছুটে আসছে। গাফলত ও নাফরমানির যিন্দেগি থেকে তওবা করছে; দ্বীনের উপর অবিচলতা এবং শরীয়তের প্রতি আনুগত্যের বিষয়ে আল্লাহর নামে নতুন প্রতিজ্ঞা করছে। গ্রাম-জনপদ থেকেও দলে দলে মানুষ হাযির হয়ে বাই‘আত গ্রহণ করছে । উপচে পড়া ভক্তি-মুহববতের সঙ্গে তারা তাঁকে নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত, কিন্তু উদারচিত্ত মুসলিমগণ মনভরে কয়েক দিন পর্যন্ত পুরো কাফেলার, এমনকি নিকটবর্তী এলাকা থেকে আসা বিপুলসংখ্যক মানুষেরও মেহমানদারি করছে। অবস্থা এমন ছিলো যে, মেযবানির জন্য লটারী করতে হয়েছে। যারা বিত্তশালী তারা রাজোচিত বদান্যতার সঙ্গে দ্বীনের পথে সম্পদ লুটিয়েছেন। এলাহাবাদের শেখ গোলাম আলী পনের দিনে সে যুগের বিশহাজার টাকা ব্যয় করেছেন।
সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ইছলাহ ও সংশোধনের এমন স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা ছিলো যে, কোন জনপদে এমন লোক খুব কমই ছিলো যারা সৈয়দ ছাহেবের হাতে তওবা করে বাই‘আত হয়নি। এলাহাবাদ, মির্যাপুর, বেনারশ, গাযীপুর, আযীমাবাদ, পাটনা ও কলকাতায় কয়েক লাখ মুসলমান তাঁর হাতে বাই‘আত ও তওবা গ্রহণ করেছে। সবচে’ চমকপ্রদ ঘটনা হলো, বেনারশ হাসপাতাল থেকে রোগিদের বার্তা এসেছিলো যে, আমাদের তো নড়াচড়ার শক্তি নেই। আপনি যদি একটিবার অনুগ্রহ করতেন, আমরা আপনার হাতে তওবা ও বাই‘আত নিয়ে ধন্য হতাম।
সৈয়দ ছাহেব খুশিমনে তাদের আবদার কবুল করেছিলেন, আর রোগীরা কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর হাতে বাইআত হয়েছিলো।
কলকাতায় তিনি দু’মাস অবস্থান করেছেন। তখন দৈনিক একহাযারে -র বেশী নারী-পুরুষ বাই‘আত হতো। সমাগমবৃদ্ধির অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিলো যে, ভোর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত বাই‘আতের সিলসিলা জারি থাকতো। সৈয়দ ছাহেবের সামান্য বিশ্রাম গ্রহণেরও অবকাশ ছিলো না। জনে জনে বাই‘আত তো সম্ভবই ছিলো না। মানুষ উন্মুক্ত স্থানে একত্র হতো। আট-দশটি পাগড়ি খুলে দেয়া হতো। মানুষ পাগড়ি ধরে রাখতো। তিনি উচ্চ স্বরে বাই‘আতের শব্দ উচ্চারণ করতেন, আর লোকেরা তা অনুকরণ করতো। এভাবে প্রতিদিন সতেরো আঠারো বার বাই‘আতের মজলিস হতো।
সৈয়দ ছাহেব পনের বিশদিন বাদফজর ওয়ায করেছেন। সাধারণ মানুষ তো ছিলো বেশুমার, ওলামা-মাশায়েখ ও নেতৃস্থানীয় লোকদেরই উপস্থিতি হতো দু’হাজারের উপরে। তাঁর সফরসঙ্গী মাওলানা আব্দুল হাই ছাহেবের ওয়ায হতো প্রতি জুমু‘আ ও মঙ্গলবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। মজমায় তিলধারণের- ও স্থান থাকতো না। প্রতিদিন দশ পনেরজন অমুসলিম তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করতো। ইছলাহ ও সংশোধন, তওবা ও আত্মশুদ্ধি এবং ব্যাপক আখেরাতমুখিতার এমনই সুফল দেখা দিলো যে, ইংরেজশাসনের কেন্দ্রস্থান কলকাতায় মদের ব্যবসায় ধ্বস নামলো। শরাবখানার জলসা ও জৌলুস শেষ হয়ে গেলো, আর মদের কারবারীরা বাজারমন্দা বলে সরকারকে রাজস্ব দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো।
হজ্ব-ফেরত কাফেলা যখন রায়বেরেলীর উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে রওয়ানা হলো তখন পথে পথে আরো অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হলো। মুরশিদাবাদে দেওয়ান গোলাম মুরতযা এমন শানদার মেহমানদারি করলেন যা এখন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। তিনি বাজারে ঘোষণা দিলেন, ‘কাফেলার যিনি যে দোকানে যা কিছু খরিদ করবেন তার মূল্য আমি পরিশোধ করবো।’
সৈয়দ ছাহেব আপত্তি করলে গোলাম মুরতযা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, হযরত, হাজিদের খিদমতের সুযোগ পাওয়া তো ফখর ও শোকরের বিষয়।
সৈয়দ ছাহেব যখন জিহাদের ডাক দিলেন তখন সর্বস্তরের মুসলিমগণ বিপুল উদ্দীপনায় তাতে সাড়া দিলো। কৃষক লাঙ্গল ছুঁড়ে, দোকানী দোকান ছেড়ে, চাকুরিজীবী চাকুরি ত্যাগ করে, ওলামা-মাশায়েখ মাদরাসা-খানকাহ থেকে বের হয়ে জিহাদি কাফেলায় শামিল হলেন এবং এমনভাবে স্বজন-স্বদেশ ত্যাগ করলেন যে, আর পিছনে ফিরে তাকালেন না। শেষ পর্যন্ত এই জানবায মুজাহিদীনের আখেরি জামাত দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী বালাকোটের দুর্গম পাথুরে উপত্যকায় দশগুণ শক্তির দুশমনের মোকাবেলায় লড়াই করে শহীদ হলেন। এমনকি শাহাদতের সময়ও তাদের মনে পড়েনি বাড়ীঘর ও আপনজনের কথা; মনে পড়েছে শুধু জান্নাতে পাখী হয়ে উড়ে বেড়ানোর খোশখবরির কথা।
এসব কিছু এমন সময় ঘটেছিলো যখন হিন্দুস্তানে ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিমশাসন ছিলো মুমূর্ষু অবস্থায়। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের দিকে দিকে একে একে বাতিগুলো যখন নিভছে, আর হতাশার ঘোর আঁধার এমনভাবে ঘিরে ধরছে যে, মুক্তির কোন উপায় দেখা যায় না। বলাবাহুল্য যে, এটা সম্ভব হয়েছে শুধু সেই দ্বীনী গায়রাত ও জাযবা, জোশে জিহাদ ও শাওকে শাহাদাত, দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, আল্লাহর রাস্তায় জান-মাল কোরবান করার আকুতি এবং সেই আখেরাতমুখিতা ও আল্লাহ-অভিমুখিতার গুণে যার ছিটেফোঁটা তখনও মুসলিম সমাজে বাকি ছিলো।
ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকেও অবস্থা এই ছিলো যে, পাশ্চাত্যের শিক্ষা-সভ্যতা, নীতি-নৈতিকতা ও শাসন-শোষণের দুষ্ট প্রভাব হিন্দুস্তানের সাধারণ জীবনে তখনো তেমন করে দেখা দেয়নি, বরং পূর্ববর্তী যুগের ছাপ ও প্রভাব তখনো বিদ্যমান ছিলো, যদিও তার ঊর্ধ্বশ্বাস শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তাই হযরত মাওলানা ফযলুর-রহমান গাঞ্জে মুরাদাবাদীর মত বুযুর্গ (রহ.১২১৩- ১৩০৮ হি.), যিনি উভয় যুগের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন, তখনকার দ্বীনী বরবাদির উপর ‘অশ্রুপাত’ করে বলতেন, ‘যাদের হাতে ছিলো হৃদয়-ব্যাধির আরোগ্য, তারা হায়, আজ সাজিয়ে বসেছে পণ্যের পসরা।’
তবে যদিও হেমন্তের বাতাস বইতে শুরু করেছিলো, তবু সবুজ পাতা সব তখনো ঝরে পড়েনি এবং বৃক্ষ একেবারে শুকিয়ে যায়নি। ডালে কিছু রস এবং পাতায় সবুজের কিছুটা আভাস তখনো ছিলো, কিংবা বলুন, বসন্ত বিদায় হলেও তার রেশ তখনো ছিলো এবং বাগানে ছিলো একটা দু’টো ফুল। আল্লাহকে পাওয়ার ব্যাকুলতা তখনো ছিলো। ইছলাহ ও সংশোধন এবং আধ্যাত্মিক সাধনা ও রূহানিয়াতের মেহনত-মুজাহাদা তখনো যিন্দেগির জরুরি বিষয় ছিলো। আহলে ইলম ও আহলে দ্বীন তো বটেই, দুনিয়ার কারবারী লোকেরাও এ চিন্তা-ব্যাকুলতা থেকে বঞ্চিত ছিলো না। তদ্রূপ বড় বড় শহর-জনপদ তো বটেই, ছোট ছোট গ্রাম-বস্তিও আল্লাহ-প্রেমিকদের দ্বারা আবাদ ছিলো। আল্লাহর মারেফাত ও পরিচয় শিক্ষা দেয়ার এবং আল্লাহর পথে আহবান করার মত সাধক পুরুষ সর্বত্র এত প্রচুর ছিলেন যে, সম্ভবত কোন স্থান ও কালই তাঁদের নূরানিয়াত থেকে মাহরূম ছিলো না। আজ থেকে অর্ধশতক আগেও বিশাল ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছিলো প্রদীপ, আর প্রদীপ; শুধু আলোর প্রদীপ! কিন্তু সারা রাত জ্বলতে জ্বলতে শেষরাতে এই প্রদীপগুলো একে একে নিভতে শুরু করেছিলো। প্রদীপ থেকে প্রদীপের আলোগ্রহণ তো আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কিছু প্রদীপ যে নিভু নিভু জ্বলছিলো তাও নিভে গেলো। অন্ধকারের সামনে সামান্য আলোর যে দুর্বল প্রতিরোধ ছিলো তাও শেষ হয়ে গেলো। চারদিকে এখন শুধু অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার।
শীতের মরা গাছে ঝাঁকুনির কী প্রয়োজন! শুকনো পাতা তো এমনিতেই ঝরে যায়! তাই বৃটিশ রাজের পক্ষ হতে এমন ঘোষণা কখনো আসেনি যে, মাদরাসা-খানকাহ বন্ধ করো। ইলমের শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক দীক্ষার ধারা চলে আসছে তার পাতা উল্টে দাও। না, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা করেনি। পরিবেশ-পরিস্থিতি বরং অপেক্ষাকৃত অনুকূল ছিলো। কারণ আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো এবং দূরদূরান্তের সফর আগের চেয়ে অনেক সহজ ছিলো। কিন্তু হৃদয়ের উত্তাপ ও দিলের তড়প যদি শেষ হয়ে যায়! সেই শওক ও জাযবাই যদি না থাকে, যা তালিবীনকে বুখারা সমরকন্দ থেকে পথের কষ্ট ও ক্ষুধা-অনাহার সহ্য করে চলে আসতে উদ্বুদ্ধ করতো!
বৃটিশরাজ এত নির্বোধ ছিলো না যে, গাছের গোড়ায় কুড়াল চালাবে এবং বাগানে আগুন লাগাবে। তারা শুধু এটা নিশ্চিত করেছে যে, গাছের গোড়ায় যেন পানি না থাকে। বুড়ো মালী বাগানের যত্ন ও পরিচর্যা যেন করতে না পারে। অর্থাৎ অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তারা শুধু নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ‘আলো’ জ্বেলে দিলো। বস্ত্তত ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থাই ছিলো হিন্দুস্তানে মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই অদৃশ্য হানাদার বাহিনী যা ‘কতল-কিতাল’ ও খুনখারাবি ছাড়াই ময়দান জিতে নিয়েছিলো এবং কাঙ্ক্ষিত ফল এনে দিয়েছিলো। এই বৃটিশশিক্ষা ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজের, বলতে গেলে প্রায় অজ্ঞাতসারেই জীবনব্যবস্থা ও চিন্তাধারা আমূল পাল্টে দিয়েছিলো। দ্বীনী চেতনা ও ধর্মীয় প্রেরণা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, দিলের ‘অঙ্গার’ ও হৃদয়ের অগ্নিফুলকি ছাইভষ্মের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো, রূহানিয়া- তের শামা’ ও আধ্যাত্মিকতার দীপশিখা নিভে গিয়েছিলো। উদ্যম-উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার স্বভাব প্রবণতা, যা জীবনের যে কোন অঙ্গনের গতি ও অগ্রগতির মূল শক্তি, তা দ্বীন ও রূহানিয়াত এবং ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে জীবিকা এবং ভোগ ও বস্ত্তর দিকে ঘুরে গিয়েছিলো। ইলমের চর্চা এবং কলবানিয়াত ও রূহানিয়াতের মেহনত-মোজাহাদার প্রতি উদ্বুদ্ধকারী উপাদানগুলো নির্জীব হয়ে পড়েছিলো, আর বিপরীত উপাদানগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলো। মেধা, প্রতিভা ও সৃজনশক্তি, যা এত দিন ধর্মচর্চা ও আধ্যাত্ম-সাধনায় নিয়োজিত ছিলো, তা জাগতিক জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে চলে গিয়েছিলো। তখন কী হলো? গাছে ফুল আসা, ফল ধরা বন্ধ হলো; ডালপালা শুকিয়ে গেলো, পাতাসব এমনিতেই ঝরে গেলো। এভাবে চোখের সামনে গোটা বাগান উজড়ে গেলো।
দ্বীনের তলব, ইছলাহে নফস ও আত্মসংশোধনের স্পৃহা, আখেরাত- মুখিতা ও আল্লাহ-অভিমুখিতা, এগুলোর জন্য মানুষের জীবনে আর কোন অবকাশই ছিলো না। হৃদয় ও আত্মা এবং কলব ও রূহের স্থানও দখল করে নিয়েছিলো উদরসর্বস্ব চিন্তা ও ভোগের উদগ্র চাহিদা। যিন্দেগির বুলন্দ মাকছাদ এবং জীবনের সুউচ্চ চিন্তা-চেতনা জাগতিক দৌড়ঝাঁপের নীচে চাপা পড়ে গিয়েছিলো। মা-হাওল ও পরিপার্শ্ব যেন কবির ভাষায় আর্তনাদ করছিলো-
‘যারা ছিলো আহলে দিল, তালাশ করো না তাদের। মরে গেছে নদী, হারিয়ে গেছে স্রোত। দরদের পণ্য ছিলো যে কিশতিতে তা ডুবে গেছে সেই কবে!’
এটা অবশ্য ঠিক যে, বিগত যুগের দ্বীনী গায়রত এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিক চেতনার মৃত্যু তখনো চূড়ান্ত হয়নি, কিছুটা প্রাণস্পন্দন বাকি ছিলো এবং বেঁচে থাকার শেষ চেষ্টা অব্যাহত ছিলো। কতিপয় কঠিনপ্রাণ দ্বীনী ব্যক্তিত্ব মৃত্যুশয্যায় নিশ্চল অবস্থায়ও দ্বীনী দাওয়াত ও রূহানি তারবিয়াতের মেহনত ধরে রেখেছিলেন এবং আত্মশোধন ও চরিত্রসংশোধনের প্রচেষ্টা ক্ষীণ ধারায় হলেও প্রবহমান রেখেছিলেন। দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি, আখেরাতের প্রতি অনুরাগ এবং সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে শাব্দিক অর্থেই তাঁরা ছিলেন সালাফের শেষ স্মৃতিচিহ্ন। মানুষ তাঁদের দাওয়াতে তখনো কিছু না কিছু সাড়া দিতো এবং মনে করতো যে, এই পাকীযা মানুষগুলোর সঙ্গে জুড়ে থাকা, অন্তত ভক্তি-শ্রদ্ধার সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে দ্বীনের আদনা হক এবং জীবনের ন্যূনতম দাবী। তারা সেটা রক্ষা করার চেষ্টা করতো। এমনকি দুনিয়াদারিতে ও বিত্তসম্পদের দৌড়ঝাঁপে ব্যতিব্যস্ত অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও আখেরাত-চিন্তায় মশগুল ছিলো এবং নফসের ইছলাহ, হৃদয় ও আত্মার সংশোধ এবং আখেরাতের সুপরিণতি ও সুন্দর মৃত্যু লাভের বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতো। কিন্তু এসবই ছিলো নিভু নিভু প্রদীপের শেষ জ্বলে ওঠা। কারণ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিলো। কিংবা বলুন, বৃক্ষের শেকড় মাটি থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলো এবং লুহাওয়া বাগান সারখার করে ফেলেছিলো।
সাধারণভাবে পুরা ইলমী ও দ্বীনী মহল এবং বিশেষভাবে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের অধিকারী খান্দানগুলোও পরিবেশের চাপে এবং ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম ও পরকাল সম্পর্কে দ্বিধা-সংশয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। আল্লাহর যাত-সত্তা ও গুণ-ছিফাতের প্রতি এবং আখেরাতের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির প্রতি আস্থা-বিশ্বাসে ফাটল ধরে গিয়েছিলো। তাই তারাও দ্বীনী তালিম ও তারবিয়াতের বিষয়ে কুণ্ঠিত ছিলো। কোরআন-সুন্নাহর ইলম হাছিল করে আলিমে দ্বীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের নামে সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে তারা আর প্রস্ত্তত ছিলো না। তাই সন্তানদের তারা জীবিকামুখী জাগতিক জ্ঞান, তথা ইংরেজি শিক্ষা প্রদানের পথেই অগ্রসর হলো। অবশ্যই তাদের এ উদ্যোগ কল্যাণকর জ্ঞান অর্জনের প্রেরণা, বা ইসলাম-রক্ষার চেতনার কারণে ছিলো না, বরং ছিলো দ্বীনের প্রতি উদাসীনতা, ভবিষ্যত সম্পর্কে দুশ্চিন্তা এবং পরিবর্তিত সময়ের কাছে আত্মসমর্পণের পরাজিত মানসিকতার কারণে। তাদের আশঙ্কা ছিলো যে, এখনো যদি কলিজার টুকরো সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষার ছেঁড়া চাটাইয়ে বসিয়ে রাখা হয়, এখনো যদি আধুনিক শিক্ষার আলো গ্রহণ না করা হয় তাহলে ভবিষ্যত শেষ। বস্ত্তত দারিদ্র্যের ভয় এবং সামাজিক অমর্যাদার আশঙ্কায় তারা এমনই বেহাল ছিলো যে, ‘মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর শিকার’ হয়ে পড়েছিলো।
এভাবেই এ প্রজন্মের বিলুপ্তি ঘটলো এবং এ পাতা উল্টে গেলো। এভাবেই নূরানিয়াতপূর্ণ সুদীর্ঘ এই রূহানি ও আধ্যাত্মিক যুগের অবসান ঘটলো এবং জড়বাদ, বস্ত্তবাদ ও ভোগবাদের সর্বগ্রাসী যুগ শুরু হয়ে গেলো, আর পৃথিবী হয়ে গেলো এমন এক বাজার যেখানে বেচা-কেনা ও কেনা-বেচা ছাড়া আর কিছু ছিলো না।
উদর ও বস্ত্তর উদগ্রতা
আজকের যুগ হৃদয় আত্মার যুগ নয়, উদর ও বস্ত্তর যুগ। জীবন এখন কোনভাবেই আখেরাতমুখী নয়, বরং দুনিয়ামুখী। আধুনিক মানুষের জীবনযাত্রায় এখন দিন-রাতের একমাত্র চিন্তা হলো, যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে পকেট ভর্তি ও উদরপূর্তি করা।
জাহেলি যুগের নারিকবি কাবশা বিনতে মা‘দীকারাব তার ভাই আমর বিন মা‘দীকারাবকে এজন্য লজ্জা দিয়েছিলেন যে, তিনি নিহত ভাইয়ের রক্তপণ গ্রহণে রাজী ছিলেন। কবিতার একটি পংক্তি দেখুন-
‘বাদ দাও আমরের কথা। সে যা করেছে তা শুধু অর্থের লোভে। অথচ তার উদর তো এক মুষ্টির চেয়ে বড় নয়!’
জাহেলিয়াতের সহজ সরল নারী কল্পনাও করতে পারেনি যে, মানুষের উদর এক মুষ্টির চেয়ে বড় হতে পারে। কিন্তু সে যদি আজকের আধুনিক মানুষের স্ফীত উদর ও থলথলে ভুঁড়ি দেখতে পেতো, যা কখনো ভরে না এবং কিছুতেই ভরাট হয় না! কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুতে যার মুখ বন্ধ হয় না!
হাঁ, পশ্চিমা সভ্যতার গর্ভ থেকে জন্ম নেয়া মানুষের লোভ-লালসার উদর এতই বড় যে, কোন পরিমাণ সম্পদই তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না এবং নদীর সব পানিও তার পিপাসা দূর করতে পারে না। তার ভিতরের জাহান্নাম থেকে লাগাতার শোনা যায় একই গর্জন, ‘হাল মিম্মাযীদ’- আরো চাই, আরো চাই! ব্যক্তি ও জাতি, উভয়ের কাঁধে লোভ-লালসার শয়তান আজ এমন চেপে বসেছে যে, উন্মাদের মত সে শুধু ছুটে চলেছে মালের পিছনে; পুরো দুনিয়াটাই যেন গিলে খাবে। হালাল-হারাম যে কোন উপায়ে সে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে চায়। তবু মনে হয় না; চাহিদা তার পুরা হয়েছে এবং অভাব দূর হয়েছে। এমন তো ছিলো না আমাদের জাতি, আমাদের সমাজ! কেন এমন হলো? কিসে এমন হলো? আসলে এটাই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার স্বভাব এবং আধুনিক জীবনের প্রকৃতি ও প্রবণতা। এ সভ্যতা, এ জীবনব্যবস্থা এমনই বস্ত্তসর্বস্ব যে, জড়জীবনের ভোগ ছাড়া আর কিছু সে বোঝে না; আখেরাত ও অনন্ত জীবনে সে বিশ্বাস করে না। তো দুনিয়ার দু’দিনের জীবন ছাড়া আর কিছু যার সামনে নেই; এ জগতের বাইরে কল্পনা-ঊর্ধ্ব আরেকটি জগত, সময় ও সীমানাহীন আরেকটি জীবন আছে বলে যার জানা নেই সে কী আর করতে পারে, বরং কী না করতে পারে! ষাট সত্তর বছরই তো তার পুঁজি! তার আশা-আকাঙক্ষার শেষ সীমা! তার জ্ঞান ও চিন্তার শেষ সীমানা! কিসের আশায়, কিসের ভরসায় বর্তমানের ভোগ-উপভোগ, স্বাদ-আহ্লাদ ও আনন্দ-ফুর্তির কোন সুযোগ হাতছাড়া করবে সে? কোন্ জীবনের জন্য, কোন্ আনন্দের জন্য, কোন্ প্রাপ্তি ও তৃপ্তির জন্য ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা এবং সাধনা ও সংযমের জীবন অবলম্বন করবে সে?
আধুনিক জীবন ও সভ্যতার এই যে ভোগবাদী ও বস্ত্তমুখী চিন্তাধারা, কোনমতেই এটা আধুনিক কিছু নয়, এটা ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতেরই উচ্ছিষ্ট মাত্র। দেখুন জাহেলী যুগের যুবক কবি তুরফা ইবনুল আব্দের কী সহজ-সরল স্বীকারোক্তি-
‘তুমি আমার আয়ু যদি বাড়াতে না পারো, মৃত্যুহীন জীবনের আশ্বাস যদি দিতে না পারো, তাহলে কেন আর কৃপণতা, কেন ত্যাগের কষ্ট, ভোগের সংযম? দাও, মৃত্যুর আগে দু’হাত ভরে আমাকে লুটতে দাও, লুটাতে দাও। যখন মৃত্যু আসবে তখন বোঝবে, কে তৃষ্ণার্ত? তুমি, না সেই উদার যুবক, জীবনকে যে সিক্ত রেখেছিলো মদ ও মদিরায়?’
আধুনিক মানুষের মত জাহেলীয়া- তের মানুষ অজুহাত ও যুক্তির আবরণে উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখা জানতো না এবং ছল ও ছলনা বুঝতো না। যা বিশ্বাস করতো সরল ভাষায় তা প্রকাশ করতো। তাই কবি তুরফা কোন রাখঢাক না করে, এত সরলভাবে মনের কথা বলতে পেরেছিলো! বস্ত্তত এটাই হচ্ছে জীবন সম্পর্কে আজকের সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। কারো তা স্পষ্ট করে বলার সাহস আছে; আর কারো মনের কথা খুলে বলার মত হয় সাহস নেই, কিংবা নেই ভাষার অলঙ্কার। জীবনের প্রতি এই বস্ত্তসর্বস্ব মানসিকতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট -সাধারণ, ধনী-নির্ধন ও অজ্ঞ-বিজ্ঞ সবাই সমান, তবে আল্লাহ যাকে ঈমানের আলো ও হিদায়াতের সুরক্ষা দান করেছেন।
দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ব্যাপক অর্থে আধুনিক সাহিত্য ও সংবাদমাধ্যম (এবং সর্বশেষ আকাশসংস্কৃতি), যা আকারে প্রকারে বিভিন্নভাবে শুধু ভোগবাদী জীবনেরই সৌন্দর্য ও মনোহর রূপ তুলে ধরে এবং এ জীবনের সফল ও বিজয়ী ব্যক্তিদের বন্দনা গায়। কলমের চাতুর্যে, ছবি ও চিত্রের কারুকার্যে এবং প্রচার- প্রচারণার মাধুর্যে বড় ঈর্ষণীয়রূপে তাদের উপস্থাপন করা হয়। গল্পের প্রতিটি চরিত্রে, নাটকের প্রতিটি অঙ্কে, গান ও কবিতার প্রতিটি স্তবকে এবং শিল্পকর্মের প্রতিটি প্রদর্শনে থাকে শুধু একই বার্তা, ‘ভোগের জন্য জীবন, জীবনের জন্য ভোগ’। বলাবাহুল্য যে, এমন বস্ত্তবাদী সাহিত্যের ছায়ায় যারা বেড়ে ওঠে, গড়ে ওঠে, পুষ্ট ও পরিপুষ্ট হয়, ভোগের উন্মাদনা ও বস্ত্তর বন্দনা ছাড়া তাদের জীবনে মহৎ ও সুন্দর কোন লক্ষ্য থাকে না। জড়বাদী পশু ছাড়া আর কোন পরিচয় সত্তাই তাদের অবশিষ্ট থাকে না।
বস্ত্তবাদী ও ভোগবাদী সমাজও একই ভূমিকা পালন করে। এ সমাজে মর্যাদা শুধু চৌকশ বিত্তশালীর জন্য, স্বভাব-চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা তার যত নিকৃষ্টই হোক। পক্ষান্তরে যার অর্থবিত্ত নেই তার কোন মান-মর্যাদা নেই; জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা ও প্রতিভা এবং স্বভাব ও চরিত্রের বিশুদ্ধতায় যত ঊর্ধ্বেই হোক তার অবস্থান। এ সমাজ আকারে ইঙ্গিতে, কখনো বা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়, ‘জীবনের উপর চিত্তহীন মানুষের অধিকার থাকতে পারে, বিত্তহীন মানুষের কিছুতেই নয়।’ এমন মানুষকে এ নিষ্ঠুর সমাজ মনে করে কুকুর-বেড়ালেরও অধম। এ অবস্থায়ও সমাজের বিরুদ্ধে যারা বুক চিতিয়ে দাঁড়াতে পারে তাদের কথা আলাদা, কিন্তু তাদের সংখ্যা কত? সময়ের চাহিদা ও প্রকৃতি মেনে নিয়ে অধিকাংশকে- ই তো সাজতে হয় সমাজের সাজে এবং চলতে হয় সমাজের পথে। তদুপরি মর্যাদা ও আভিজাত্যের মাপকাঠি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার দাবী ও চাহিদা শুধু বাড়তে থাকে। ফলে জীবনসংগ্রামে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত মানুষ আরো বেশী অর্থের জন্য আরো ভুল পথে যেতে বাধ্য হয়। আর তাতে নেমে আসে বিভিন্ন দুর্ভোগ-দুর্গতি, দুর্দশা ও বিপর্যয়, যার শুরু আছে, শেষ নেই। এর মধ্যে ‘শনির খাড়া’ হয়ে নেমে আসে চটকদার বিজ্ঞাপনের আগ্রাসন, পণ্যসামগ্রীর উৎপাদন-জোয়ার এবং পুঁজিপতি ও শিল্পগোষ্ঠীগুলোর উন্মত্ত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা ও মুনাফা-লিপ্সা। আজ যা নতুন মডেলের গাড়ী, নতুন ফ্যাশনের পোশাক এবং নতুন ডিজাইনের আসবাব দু’দিন পরেই তা হয়ে যায় সেকেলে। এভাবে যেসব জিনিস ছিলো জীবনের বাড়তি ‘ফুযুল’ তাই হয়ে পড়ে সামাজিক ও নাগরিক মর্যাদার প্রতীক। যারা তা রক্ষা করে না তারা হয়ে পড়ে সমাজে অপাংক্তেয়। এগুলোর মূলে কিন্তু প্রয়োজনের দাবী নয়, শুধু বাজার, বাণিজ্য ও মুনাফার স্বার্থ।
এসব কারণে এবং অন্য আরো অনেক কারণে অর্থবিত্তের মূল্য ও গুরুত্ব আহ এত বেড়ে গিয়েছে যে, পিছনে মানুষের লিখিত ইতিহাসে আর কখনো হয়নি। অর্থসম্পদই এখন সমাজদেহের প্রাণ এবং যাবতীয় নাগরিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি, বরং এটাই একমাত্র অক্ষদ- যার উপর আবর্তিত হচ্ছে আধুনিক জীবনের চাকা। লন্ডনবিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন ও মনস্তত্ত্বের অধ্যাপক জুড যা বলেছেন তা শুধু ইউরোপের ক্ষেত্রেই নয়, পশ্চিমা সভ্যতার আগ্রাসনের শিকার প্রতিটি সমাজ সম্পর্কেই সমান প্রযোজ্য। তিনি বলেন, ‘যে জীবনদর্শন বর্তমান যুগের উপর অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে তা হলো অর্থনৈতিক দর্শন। ‘পেট ও পকেট’ই এখন যে কোন বিষয়ের প্রতি মানুষে আগ্রহ-অনাগ্রহের মাপকাঠি।’
আপনি যদি যুগ ও সমাজের রুচি, স্বভাব ও গতি-প্রকৃতি বিচার করেন বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং ঐ সকল গবেষণাপত্রের সাহায্যে, যা গৃহের নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে বাস্তবতার পরিবর্তে তাত্ত্বিকতার ভিত্তিতে লেখা হয়েছে তাহলে অবশ্যই আপনি ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির শিকার হবেন। কেননা লেখক, সাহিত্যিক ও দার্শনিকগণ কখনো কখনো ব্যক্তির রুচি-প্রবণতা এবং ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। কখনো বা বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে নিজস্ব আশা ও প্রত্যাশার চিত্র তুলে ধরেন। অর্থাৎ যা ঘটেছে বা ঘটছে তার পরিবর্তে যা ঘটা কাম্য তাই লিখে থাকেন। যদিও লেখার আয়নায় সমাজের বিদ্যমান রুচি ও প্রবণতার কিছু না কিছু ছাপ পড়েই থাকে, তবু সাধারণ অবস্থা এটাই যে, এতে ভুল সিদ্ধান্তের প্রবল ঝুঁকি থাকে। তাই যুগ ও সমাজের রুচি, অভিরুচি এবং ঝোঁক ও প্রবণতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে বইয়ের পাতা থেকে নয়, জীবনের পাতা থেকেই পেতে হবে। মানুষের সঙ্গে মিশে আপনাকে তাদের ঘরোয়া কথা-বার্তা ও মজলিসি আলাপ শুনতে হবে। সেখান থেকেই বেরিয়ে আসবে যুগ ও সমাজের প্রকৃত চিত্র। আকবর যেমন বলেছেন তার কবিতায়-
‘চিত্র ও মানচিত্র দেখে বিচার করো না, মানুষের ভিতরে গিয়ে দেখো, কী জীবন্ত আছে, কী বিলুপ্ত হয়েছে।’.
এ মাপকাঠির ভিত্তিতে আপনি গাড়ী ও রেলগাড়ীর সফরে, সকাল-সন্ধ্যার ভ্রমণে, চায়ের মজলিসে, পার্কে-উদ্যানে এবং বন্ধুমহলে কান পেতে শুনুন, কী নিয়ে কথা হচ্ছে, কী নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে?! যে কোন আলোচনার শুরু কোত্থেকে এবং শেষ কোথায়? আপনার কানে আসবে শুধু এপার-জীবনের আলাপ; ওপার-জীবনের কোন আলোচনাই সেখানে নেই, একদু’টি ব্যতিক্রম ছাড়া।
আরব কবি ভিক্ষুককে অভিসম্পাত দিচ্ছেন এজন্য যে, তার নযর কখনো রুটি-কাপড়ের উপরে ওঠে না। দেখুন- ‘সেই ভিক্ষুকের আল্লাহ সর্বনাশ করুন, যার চিন্তা ও দুশ্চিন্তা হলো একটুকরো রুটি, আর একখ- কাপড়।’
এই জাহেলী কবি যদি আজকের ‘সভ্য জীবন’ দেখতে পেতেন, যেখানে দার্শনিক ও রাজনীতিক এবং বিচারপতি ও পুঁজিপতি কারো চিন্তাই রুটি-কাপড় অতিক্রম করতে পারে না তাহলে তিনি কী বলতেন?!
আকারে, প্রকারে, আবরণে ও অলঙ্কারে যতই ভিন্নতা থাকুক; বিষয় কিন্তু একই, সোনা-চাঁদি ও রুটি-কাপড়। পশ্চিমা বিশ্বকে বলা যায় এ নতুন জীবনদর্শনের স্রষ্টা, আর অন্যান্য জাতি হলো তাদের অনুগামী, কিন্তু আফসোস, মুসলিমজাতিও আজ তাদেরই পদ-রেখার অনুসারী!
নীতি ও নৈতিকতার ধ্বস
ইসলামী প্রাচ্যে পশ্চিমারা যখন প্রথমে বণিকবেশে, তারপর শাসক ও শোষকরূপে তাদের দখলদারি কায়েম করে তার আগে থেকেই সেখানে নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয় শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং প্রাচ্য ও ইসলামী সভ্যতার গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো বিনষ্ট হতে শুরু করেছিলো, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলো মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পতন এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীগুলোর অধঃপতন।
এত কিছুর পরো নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তখনো তাদের মধ্যে এমন কিছু নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো এবং তা এতটাই উচ্চস্তরের ছিলো যার নমুনা অন্যান্য জাতির নৈতিক ইতিহাসে নেই। প্রাচ্যের অধিবাসিগণ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যর উৎকর্ষ সাধন করে করে সেটাকে রীতিমত একটি কলা ও সংস্কৃতির রূপ দান করেছিলেন এবং তাতে এমন এমন সূক্ষ্মতা, কমনীয়তা ও লালিত্য আনয়ন করেছিলেন যা পশ্চিমে শুধু কবিতা ও সাহিত্যে এবং শিল্পকলায় ভাবা যায়, জীবনের আচরণে নয়।
ইসলামী প্রাচ্যে মানুষের মধ্যে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন এমনই সুগভীর, সুসংহত ও সুদূরপ্রসারী ছিলো যা এযুগে কল্পনারও বাইরে। সর্বোপরি এসকল সম্পর্ক ছিলো সর্বপ্রকার জাগতিক স্বার্থ ও বস্ত্তগত লাভের ঊর্ধ্বে, যেখানে পাশ্চাত্যে প্রতিটি সম্পর্ক নির্ধারিত হয় সুযোগ সুবিধার উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে। মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের এবং সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার ভালোবাসা ও মায়া-মমতার যে বন্ধন, ছোট ও বড়ের মধ্যে সেণহ-সম্মানের যে সম্পর্ক, নারীর সতিত্ব, দাম্পত্য-বিশ্বস্ততা, চাকর-নওকরদের আমানতদারি ও নিমকহালালি, যুবকদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, শরীফ ও অভিজাত শ্রেণীর পারস্পরিক আচরণে সমতা ও শিষ্টাচার এবং বন্ধুর জন্য বন্ধুর ত্যাগ ও আত্মত্যাগ, এসকল ক্ষেত্রে এমন এমন ঘটনা রয়েছে যা এখন মনে হয় কাহিনী, আর কিছু দিন পর মনে হবে অলীক কাহিনী। বস্ত্তত প্রাচ্যের ইসলামী পরিবারে বৃদ্ধ পিতা-মাতাই ছিলেন সবচে’ শ্রদ্ধার পাত্র। তাদের পরিপূর্ণ সেবা-যত্ন ও সন্তুষ্টি অর্জনই ছিলো গোটা পরিবারের স্বতঃস্ফূর্ত কর্তব্য। বড় বড় পারিবারিক বিষয়ে পিতা-মাতার সিদ্ধান্তই ছিলো চূড়ান্ত এবং সেটাকে মনে করা হতো কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কারণ। পশ্চিমা সমাজ ও সভ্যতা এটা কীভাবে কল্পনা করতে পারবে, যেখানে বুড়ো মা-বাবার নিঃসঙ্গ জীবন কাটে বৃদ্ধনিবাসে! মুসলিম সমাজের দুর্ভাগ্য, এখানেও এখন ‘সুন্দর সুন্দর’ বৃদ্ধ আশ্রম গড়ে ওঠছে।
প্রাচ্যে মুসলিম সমাজে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের আত্মনিবেদনমূলক এই যে সংস্কৃতি, এর উৎস হলো নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ মহান বাণী-
انت و مالك لأبيك
তুমি ও তোমার সম্পদ, সব তোমার আববার।
পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের ভালোবাসা ও ভক্তি-মুহববত এবং সেবা ও সদাচার তাদের জীবদ্দশা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তাদের মৃত্যুর পরো তা অব্যাহত থাকতো। কারণ মা-বাবার বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে সর্বপ্রকার সদাচার রক্ষা করাকেও কৃতার্থ সন্তানগণ নৈতিক কর্তব্য মনে করতো। আর এটাও মূলত নববী শিক্ষারই প্রতিবিম্ব ছিলো, যিনি ইরশাদ করেছেন, ‘মানুষের সর্বোত্তম নেক আমলের একটি হলো, মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের বন্ধু-স্বজনদের সঙ্গে সদাচার করা।’
সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা ও লালন প্রতিপালনে প্রাচ্যের ইসলামী পরিবারে মা-বাবার ত্যাগ ও আত্মত্যাগ ছিলো তুলনাহীন। সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য জীবনের সব সাধ-আহ্লাদ, আরাম-আয়েশ হাসিমুখে তারা বিসর্জন দিতেন। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য তিলে তিলে নিজেদের ক্ষয় করে দেয়া, এতেই ছিলো তাদের আত্মার শান্তি। সন্তানের তালিম-তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষাই ছিলো তাদের জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, একমাত্র লক্ষ্য। এমনকি সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনে শক্ত হতেও তারা দ্বিধা করতেন না। সন্তানকে দূরের শহরে পাঠিয়ে দিয়ে বাবা কান্না চেপে রাখতেন, আর মা আচলে চোখের পানি মুছতেন। সন্তান ‘কী না কী খায়’ ভেবে, তাদের মুখে আর ভালো খাবার উঠতো না। এমন কাহিনী প্রাচ্যের ঘরে ঘরে এত অসংখ্য যে, অন্য সমাজে, অন্য সভ্যতায় তা কল্পনা করাও ভার।
উস্তাদের শাসন ও শাস্তি কখনো সীমা লঙ্ঘন করলে মা-বাবা হাতের জ্বলন্ত অঙ্গারের মত তা বরদাশত করে নিতেন। সন্তানকে প্রশ্রয় দেয়া বা অভিযোগ করা তো দূরের কথা, উস্তাদের শানে অশোভন কোন শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করাকে ভাবা হতো শরাফত ও ভদ্রতার মানদ- থেকে নীচের বিষয়। এসব ক্ষেত্রে তারা বরং সন্তানকে প্রবোধ দিতেন যে, উস্তাদের হক মা-বাবার উপরে। কখনো বলতেন, ওস্তাদের শাসন ছাড়া কে কবে বড় হতে পেরেছে?
এক্ষেত্রে সাধারণ ও অভিজাত পরিবারে কোন পার্থক্য ছিলো না। উভয়ের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অভিন্ন, বরং অভিজাত পিতা-মাতার আচরণ হতো আরো অভিজাত। উস্তাদ কাসাঈ’র খেদমত সম্পর্কে আমীন-মামূনের প্রতি খলীফা হারুন রশীদের যে উপদেশ তার তুলনা কোথায়?
এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে বহু বিস্ময়কর
ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও মনমানসের প্রতিনিধিত্ব করে। এখানে একটি মাত্র ঘটনা শুনুন। তাজুদ্দীন আলদায, যিনি সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর পর আফগানিস্তানের শাসক ছিলেন, তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব জনৈক শিক্ষকের হাতে ন্যস্ত করলেন। সে যুগের শিক্ষকও বাদশাহযাদাকে শাসন করতে দ্বিধা করতেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, একবার তার শাসন- প্রহারে বাদশাহযাদা মারাই গেলো। কী নাযুক পরিস্থিতি! কিন্তু বাদশাহ চরম ধৈর্য-সংযমের পরিচয় দিয়ে শিক্ষককে বললেন, আপনি দূরে কোথাও চলে যান। কারণ সন্তানের মা সম্পর্কে আমি আশ্বস্ত নই। তার পক্ষ হতে যদি অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু হয়ে যায়!
ইসলামী সমাজে বড় ও ছোটের পরস্পর সম্পর্কের ভিত্তি ছিলো শরীয়াতের এই শিক্ষা-
‘যে আমাদের ছোটকে সেণহ করে না এবং আমাদের বড়কে সম্মান করে না সে আমাদের মধ্য হতে নয়।’
প্রাচ্যের সভ্যতা ও তাহযীব তামাদ্দুনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিলো আভিজাত্য রক্ষা করে জীবনকে একধাঁচে একভাবে যাপন করা। আজকের অবনতিশীল সমাজেও এক্ষেত্রে বিস্ময়কর বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে কাজ, আচরণ, রীতি বা নীতি নিজের জন্য নির্ধারণ করতো তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতো। এমনকি লেবাস-পোশাকের স্বকীয়তাও বজায় রাখার চেষ্টা করতো। পরিবেশ, পরিস্থিতি, মৌসুম ও স্বাস্থ্যের পরিবর্তনে তাতে কোন পরিবর্তন আসতো না। যার সঙ্গে যে আচরণ ও সম্পর্ক শুরু হতো, জীবনের শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করা হতো, সেজন্য যত বড় মূল্য দিতে হোক তা থেকে পিছিয়ে আসার কথা চিন্তাও করা হতো না। সে যুগে পারিবারিক ও গোত্রীয় জীবনে মর্যাদা ও সম্পর্কের ভিত্তি অর্থের প্রাচুর্য ছিলো না।খান্দানে বিভিন্ন জনে অর্থনৈতিক তারতম্য হতে পারে। কেউ সচ্ছল, বিত্তবান; কেউ অসচ্ছল, বিত্তহীন। কিন্তু খান্দানি মজলিসে এটা অকল্পনীয় ছিলো যে, অর্থনৈতিক পার্থক্যের কারণে কারো প্রতি কারো আচরণ ভিন্ন হবে। এমন ভুল ভুলেও যদি হতো, পুরা খান্দান তার প্রতিবাদ করতো, এমনকি তাকে ‘ভিন্ন’ করে দেয়া হতো, যতক্ষণ না সে মাফ চায়। একজন অসচ্ছল শরীফ ব্যক্তি তার সচ্ছল ভাই বা আত্মীয়ের সঙ্গে নিঃসংকোচে কথা বলতো এবং বলতে পারতো। কেননা আভিজাত্য, বংশমর্যাদা, নিজস্ব গুণ ও যোগ্যতা, কিংবা আত্মীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে তার সঙ্গে সমতার আচরণই করা হতো। হতে পারে, কারো জীবনে দারিদ্র্যের ছায়া পড়েছে, কিন্তু সেটা তার বংশীয় আভিজাত্য, ধর্মীয় মর্যাদা ও জ্ঞান-প্রজ্ঞাকে আড়াল করতে পারতো না।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো এই যে, অসচ্ছল ও দরিদ্র ব্যক্তি তার অসচ্ছলতা ও দারিদ্র্য সংযম ও যত্নের সঙ্গে গোপন রাখার চেষ্টা করতো। কেউ তার ঘরের অভাব-অনাহারের কথা জানবে, এটা গরীব থেকে গরীব মানুষের জন্যও ছিলো কষ্টের বিষয়। অতি নিকটজন ছাড়া কারো সামনেই প্রকাশ করা হতো না।
ইসলামী সমাজের শেষ সময় পর্যন্ত বিবেকবান মানুষের কাছে বিবেক ছিলো তার দ্বীন-ধর্ম ও ইয্যত-আবরুর মতই এমন মূল্যবান যে, কোন মূল্যেই তা খরিদ করা সম্ভব ছিলো না। ভয়-ভীতি এবং লোভ ও প্রলোভন, কোন কিছুই তাকে বিবেকের অবস্থান থেকে সরাতে পারতো না। আঠারোশ সাতান্নের মহাবিদ্রোহের আগে-পরে বহু অভিজাত মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটেছে যে, হাসিমুখে তারা মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু বিবেকের অপমৃত্যু হতে দেননি। বুক পেতে গুলি খেয়েছেন, গলায় ফাঁসির রজ্জু পরেছেন; বাঁচার জন্য এইটুকু বলাই যথেষ্ট ছিলো, ‘এ বিদ্রোহে আমি ছিলাম না’, কিন্তু মিথ্যা বলা পছন্দ করেননি। বহু উদাহরণের শুধু একটি শুনুন। শায়খ রাযিউল্লাহ বাদায়ুনী রহ. ৫৭-এর বিদ্রোহের অভিযোগে ধৃত হলেন। যে ইংরেজ বিচারকের আদালতে তাঁর বিচার হলো তিনি ছিলেন শায়খ বাদায়ুনীর ছাত্র। বিচারক কোন বন্ধুর মাধ্যমে ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি যেন অভিযোগ অস্বীকার করেন, যাতে তাকে অব্যাহতি দিতে পারি। শায়খ তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যা করেছি তা কীভাবে অস্বীকার করবো? ফলে ইংরেজ বিচারক সহানুভূতিশীল হয়েও ফাঁসীর রায় দিতে বাধ্য হলেন। এমনকি ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার সময়ও ইংরেজ বিচারক শেষ অনুরোধ জানিয়ে বললেন, এখনো সময় আছে, একবার যদি বলেন, অভিযোগ মিথ্যা, তাহলে রায় পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারি। শায়খ নারায হয়ে বললেন, তুমি কি চাও, একটি মিথ্যা দ্বারা সারা জীবনের অর্জন নষ্ট করে ফেলি! তাহলে তো নিজেই নিজের সর্বনাশ করলাম। না, আমি বিদ্রোহে ছিলাম; এটাই সত্য, যা করার করো।
ফাঁসির রজ্জুতে তিনি তো মরলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মের সত্য অমর হলো।
সত্যের প্রতি এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বাসের প্রতি এই অবিচলতা ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রেও তা অক্ষুণ্ণ ছিলো। স্বজাতি ও স্বদেশ-অন্ধত্ব বলতে কোন কিছু তাদের জীবনে ছিলো না, যা বর্তমান যুগের অপরিহার্য গুণ বলে স্বীকৃত। নিজের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি সম্প্রদায়িক স্বার্থে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাকেও তারা পাপ ও নীচতা বলে বিশ্বাস করতেন। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি, পরিবার, জাতি ও সমাজ সর্বক্ষেত্রে বিধান অভিন্ন। আল-কোরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-
‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের প্রতি একনিষ্ঠ হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী হও, যদিও তা তোমাদের, পিতা-মাতা ও স্বজনদের বিপক্ষে হয়।
‘কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন অন্যায়ের প্রতি তোমাদের প্ররোচিত না করে। সুবিচার করো; (কারণ) সেটাই হলো তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী, আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।
‘যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ইনছাফের সঙ্গে বিচার করবে।’
‘আর যখন কোন কথা বলবে তখন ইনছাফ রক্ষা করবে, যদিও তা আত্মীয়ের বিপক্ষে যায়।’
প্রাচ্যের মুসলিম জাতি তাদের এই ধর্ম-বিধানের প্রতি কতটা অনুগত ছিলো তার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় ভরপুর। এখানে আমরা শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে একটিমাত্র ঘটনা উলেস্নখ করছি। ইংরেজরাজত্বের শুরুর দিকে মুজাফফরনগর জেলার কসবা কান্ধলায় একটি ভূমি নিয়ে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ দেখা দিলো। হিন্দুদের কথা, এটি দেবসম্পত্তি, মুসলমানদের দাবী, এটি মসজিদের জমি। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট উভয় পক্ষের যুক্তি-প্রমাণ শুনে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। তখন তিনি মুসলিম পক্ষকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কোন হিন্দু সাধু কি আছেন যার সততা ও সত্যবাদিতার উপর আপনাদের আস্থা আছে, যার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফায়ছালা হতে পারে? তারা বললেন, এমন কেউ নেই।
একই প্রশ্নের উত্তরে হিন্দুরা বললো, এ তো বড় কঠিন পরীক্ষা! বিষয়টিও ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত। তবে একজন আছেন যিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। হয়ত এক্ষেত্রেও তিনি সত্যই বলবেন।
হিন্দুরা যার কথা বলেছিলো, তিনি (সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.-এর খলীফা হযরত শাহ আব্দুল আযীয দেহলবী রহ.-এর ছাত্র) মুফতি এলাহী বখশ রহ.-এর খান্দানের কোন বুযুর্গ। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে আদালতে ডেকে পাঠালেন, আর তিনি বললেন, আমি কসম করেছি, বেঁচে থাকতে কোন ফিরিঙ্গির চেহারা দেখবো না।
এমন ইংরেজও ছিলো যারা এমন কথাও হাসিমুখে গ্রহণ করতো। তিনি বলে পাঠালেন, ঠিক আছে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তবু আপনি আসুন।
তিনি আদালতে হাযির হলেন এবং ‘ফিরিঙ্গি’র দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। হিন্দু-মুসলিম উভয় পক্ষ তাঁর দিকে তাকিয়ে, আর বিচারক তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য উৎকর্ণ। কারণ তাঁরই কথায় একটি গুরুতর সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফায়ছালা হবে।
তিনি বললেন, ‘সত্য কথা বলতেই হবে। জমি মন্দিরের, মসজিদের
নয়।’
আদালতের ফায়ছালায় মুসলমানদের পরাজয় হলো, কিন্তু নৈতিক বিজয় হলো ইসলামের। ইসলামী শিক্ষার একটিমাত্র অভিপ্রকাশে একখন্ড ভূমি যদিও হাতছাড়া হলো, কিন্তু বহু হৃদয় বিজিত হলো এবং অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলো।
বিকেকের মত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাও ছিলো তাদের কাছে আল্লাহর আমানত, যা কোন মুল্যেই বাজারে পণ্যের মত বিক্রি হতে পারে না। এক্ষেত্রে যারা উচ্চস্তরের তারা তো এটাও বরদাশত করতেন না যে, অন্যায়ের পক্ষে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কোনভাবে তাদের জ্ঞান ও মেধা ব্যবহৃত হবে, কিংবা কোন যালিম শাসক ও ইসলাম-দুশমন হুকুমতের কাজে লাগবে। এটাকে তারা মনে করতেন আসমানি আমানতের সঙ্গিন খেয়ানত।
এক্ষেত্রেও ইতিহাস থেকে আমরা শুধু একটি ঘটনা বলবো। শায়খ আব্দুর-রহীম রামপুরী রহ. দেশীয় মুসলিম রাজ্যের পক্ষ হতে মাত্র দশটাকা মাসোহারায় শিক্ষক ছিলেন। এসময় রোহিলাখন্ডের ইংরেজ শাসক মিস্টার হকিন্স তাঁকে বেরেলী কলেজে আড়াইশ টাকা বেতনে শিক্ষকতার প্রস্তাব দিলেন এবং খুব দ্রুত পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিলেন। সাতান্নপূর্ব ভারতের আড়াইশ টাকা বর্তমানে কত হয় ভাবুন!
শায়খ বললেন, তাহলে তো আমার দশটাকা ভাতা বন্ধ হয়ে যাবে! মিস্টার হকিন্স হতচকিত হয়ে বললেন, আজিব মানুষ! আড়াই শ টাকার বদলে দশটাকার আফসোস!
শায়খ তখন বললেন, তাছাড়া আমার বাড়ীতে একটি বরই গাছ আছে, যার বরই আমার খুব প্রিয়। বেরেলীতে তা পাবো কোথায়?
বেচারা ইংরেজ যে কোন উপায়ে শায়খের সেবা পেতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, সে ব্যবস্থা আমি করবো।
শায়খ তখন বললেন, আরেকটা সমস্যা আরেকটু গম্ভীর। রামপুরে যারা আমার কাছে পড়ে, আমি চলে গেলে তাদের পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। মিস্টার হকিন্স তখনো হাল ছাড়তে রাজী নন, তিনি বললেন, তাদের জন্য বৃত্তি মঞ্জুর করা হবে, যাতে তারা আপনার কাছে পড়া অব্যাহত রাখতে পারে।
শায়খ তখন তাঁর তূণীরের শেষ তীরটি ছুঁড়লেন যার কোন জবাব ইংরেজ-পুত্রের কাছে ছিলো না। তিনি বললেন, সব ঠিক আছে। কিন্তু আগামীকাল আল্লাহ যখন জিজ্ঞাসা করবেন, বেশী মূল্যে ইলম বিক্রি করেছো, তখন কী জবাব দেবো?!
বিজয়ী জাতির শাসক অবশেষে মুসলিম আলিমের অনুভূতি বুঝতে পেরে অভিভূত ও শ্রদ্ধাবনত হলেন। এদিকে শায়খ সেই দশটাকা মাসোহারায় সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাঁকে করুণা করুন, আর আমাদের চলার পথ আলোকিত করুন।
এই সমুচ্চ নীতি ও নৈতিকতার তুলনা করুন বর্তমান যুগের জ্ঞান-বাণিজ্যের সঙ্গে। জ্ঞানজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে এখন রীতিমত নিলামে তুলে দিয়েছেন। সর্বোচ্চ দরে বিক্রি হয় তাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির পণ্য, ক্রেতা যেই হোক এবং তার পরিচয় যাই হোক। আকীদা, বিশ্বাস, উদ্দেশ্য ও ফল, এমনকি রুচি ও মানসিকতার বিষয়টিও এখন গৌণ: মূল্যই হচ্ছে মূল বিষয়। এক্ষেত্রে নিত্যনতুন এমন সব ঘটনার জন্ম হচ্ছে যা একদিকে হাসির খোরাক যোগায়, অন্যদিকে চোখে পানি আনে। কোন ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি একশ দেয়, আর কোন মিশনারি প্রতিষ্ঠান দেয় দেড়শ তাহলে নির্দ্বিধায় একজন শিক্ষক প্রথমটি ছেড়ে দ্বিতীয়টিতে চলে যাবেন। এমন ঘটনাও আছে যে, শিক্ষাবিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত শিক্ষিত যুবক, যার ঐ বিভাগে সৃজনশীল কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ-সম্ভাবনা ছিলো, হঠাৎ তিনি পুলিশে বা কাস্টমসে বদলি হয়ে গেছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন জীবনের এই হঠাৎ মোড় পরিবর্তন? তার সরল স্বীকারোক্তি, ‘এখানে পয়সা বেশী।’
আরেকজন স্কলার ইসলামী
তাছাওউফের উপর গবেষণাপত্র লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন, হঠাৎ শুনি, তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে যোগ দিয়েছেন; সেখান থেকে আবার চলে গেছেন দোভাষীর কাজে কোন ইউরোপীয় দেশে। উদ্দেশ্য, অধিকতর সুবিধা অর্জন। সুবিধাই যেন জীবন; অর্থই যেন পূজ্য। হৃদয় ও আত্মার উপর এবং জ্ঞান-গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তির উপর মুদ্রা ও স্বর্ণমুদ্রারই এখন একচ্ছত্র প্রভাব।
ইতিহাসে আমরা পড়েছি, প্রসিদ্ধ আববাসী খলীফা আলমানছূর একবার কিছু লেখার জন্য মজলিসে উপস্থিত ইবনে তাউসকে কালির দোয়াত এগিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু ইবনে তাউস বিরত থাকলেন। ক্ষুব্ধ খলীফা ‘আমীরুল মুমিনীন’-এর হুকুম না মানার কারণ জানতে চাইলেন। ইবনে তাউস বললেন, আমার আশঙ্কা, এ কালি দিয়ে কোন না-হক ফরমান লেখা হবে, আর আমিও তাতে শামিল হয়ে যাবো।
এমনই চূড়ান্ত স্তরে ছিলো এই কোরআনি আদেশের উপর তাঁদের আমল-
‘তোমরা পুণ্যকর্ম ও ধার্মিকতায় পরস্পর সহযোগিতা করো, পাপ ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পর সহযোগিতা করো না।’
আর ইসলামের সোনালী যুগে তো এমন ঘটনা ছিলো প্রচুর ও নিশ্চিত সনদে বর্ণিত যে, ওলামায়ে উম্মত শত প্রলোভন ও ভীতিপ্রদর্শনের মুখেও ঐ শাসকের অধীনে বিচারক হতেও রাজী হননি যার নীতি ও কর্মনীতির প্রতি তিনি আশ্বস্ত নন।
অন্যায়কর্মে কোন প্রকার সহযোগিতা করা, অস্বচ্ছ প্রশাসনের অধীনে কোন পদ গ্রহণ করা এবং মুসলিম উম্মাহর স্বার্থবিরোধী কোন কাজে কোনভাবে সংশ্লিষ্ট হওয়া দূরের কথা, এসবের স্পর্শ থেকেও বেঁচে থাকার এই যে সর্বাত্মক সতর্ক প্রচেষ্টা, এর সঙ্গে বর্তমান যুগের মুসলিমদের অবস্থা তুলনা করুন, যারা ইউরোপের বিভিন্ন সরকারের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে; সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে যাদের মেধা, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষুরধার লেখনীশক্তি অমুসলিম দেশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের অনুকূলে, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মুসলিম স্বার্থের প্রতিকূলে ব্যবহৃত হচ্ছে। তুলনা করুন এবং বিচার করুন, আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় নেমে এসেছি!
মুসলিম বিশ্বের বহু যুবক ও প্রতিষ্ঠিত লেখক বিভিন্ন দেশের ও দূতাবাসের পক্ষ হতে স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় কাজ করে, যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে মুসলিম দেশে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং মুসলিম চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসে প্রভাব বিস্তার করা। ভাড়াটে মুসলিম লেখক-বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমেই তারা মুসলিম বিশ্বে তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাপ্রচারণার কাজটি করে থাকে।
আরববিশ্বে এমন বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত আছেন যারা অভিজাত ও ঐতিহ্যবাহী আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্য ঐ সব পরিবারের বিরাট ত্যাগ ও কোরবানি রয়েছে। তাদের পদবীও ঐ রক্তের উত্তরাধিকার প্রমাণ করছে, কিন্তু তারা আজ ইউরোপের বিভিন্ন সরকারের অধীনে তাদেরই স্বার্থের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করছেন। কালামুল্লাহ-এর আরবীভাষা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অমুসলিমদের স্বার্থ-সেবায়, যে ভাষায় মুসলিম উম্মাহর প্রতিনিধিগণ একসময় রোম ও পারস্যের রাজদরবারে নির্ভীকচিত্তে কথা বলেছেন এবং ভীতি ও সমিহ আদায় করেছেন। যে ভাষায় ইতিহাসে অমর মুসলিম সেনাপতিগণ জিহাদের অনলবর্ষী ভাষণ দিয়েছেন। যে মহান ভাষা শুধু ইসলামী শৌর্য-বীর্য প্রকাশেরই উপযোগী এবং যে অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাগ্মিতা শুধু জিহাদের ঘোষণা ও সত্যের বার্তা প্রচারের জন্যই শোভনীয়, তা আজ ব্যবহৃত হচ্ছে অমুসলিম সরকারগুলোর প্রচার-প্রচারণার কাজে, যারা মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে এমনই খেলছে, যেমন খেলে কোন খেলোয়াড় পায়ের বল নিয়ে; যারা মুসলিম বিশ্বের ঈমান ও বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং সম্পদ ও অর্থনীতির সর্বনাশ সাধনে সদা তৎপর।
আরো লজ্জাকর বিষয়, এই জ্ঞান- পাপীরা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে থাকেন, ‘অমুসলিম হলেও ওরা আরব ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি আন্তরিক। আমাদের কল্যাণে ওরা নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছে।’
আরো বলতে শোনা যায়, ‘বিবিসি’র বিশাল সম্প্রচার কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আরব-জাগরণ, আরবসংহতি এবং আরববিশ্বের চিন্তানৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন। আরো উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাহকে তাদের গৌরবময় ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত করা এবং সততা, সত্যতা ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির বাস্তবতা তাদের সামনে তুলে ধরা।’
দীর্ঘ দিন থেকেই তাদের এ বক্তব্য আমরা শুনে আসছি যে, ওরা বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাবিধানে তৎপর, সর্বোপরি দুর্বল জাতি ও রাষ্ট্রবর্গের স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিত করার বিষয়ে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট। ন্যায় ও সাম্যের পতাকা সমুন্নত রাখা এবং যালিমের বিরুদ্ধে মযলুমের পক্ষাবলম্বন করাই হচ্ছে তাদের লক্ষ্য ...’
এখন কথা হলো, তারা যা বলছেন, তাতে যদি তাদের বিবেকের সায় না থাকে বরং তাদের যদি জানা থাকে যে, এসব শব্দ যথাপাত্রে প্রযুক্ত নয়, বরং শুধু অর্থ ও স্বার্থের কালিমা আড়াল করার হীন উদ্দেশ্যে উচ্চারিত তাহলে তো বলতে হয়, মহৎ প্রাণের একি অধঃপতন! মহামূল্য পণ্যের একি দরপতন! আরবের হাতে আরবী ভাষার একি লাঞ্ছনা!
আর যদি পূর্ণ বিশ্বাস ও উপলব্ধি হতে বলে থাকেন তাহলে বলতে হয়, সত্য ও বাস্তবতা সম্পর্কে একি অজ্ঞতা! বোধ ও বুদ্ধির একি ভ্রষ্টতা! হৃদয় ও আত্মার একি অপমৃত্যু!
আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির যুগ যেন আগাগোড়া স্ববিরোধিতার যুগ। তাই দেখা যায়, কোন লেখক-সাংবাদিক হয়ত আজ মুসলিম উম্মাহর কোন বীর মুজাহিদ ও বরণীয় ব্যক্তি সম্পর্কে উদ্দীপনাপূর্ণ কিছু লিখেছেন, কিন্তু লেখার কালি না শুকোতেই নিছক স্বার্থের খাতিরে মুসলিম উম্মাহর কোন দুশমন ও গাদ্দারের পক্ষে কলম ধরেছেন!
পক্ষান্তরে প্রাচীন যুগের দৃশ্য দেখুন, এক আরব বাদশাহ জনৈক আরব কবির কাছে তার ঘোড়াটি চাইলেন, আর তিনি কোন মূল্যেই তা দিতে অস্বীকার করে কবিতা লিখলেন-
‘আপনি শাপমুক্ত থাকুন, আমার ঘোড়া ‘সিকাব’ তো এমন মূল্যবান সম্পদ যা না ধারে দেয়া যায়, না বিক্রিতে।’
কিন্তু এ যুগে যারা নিজেদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি অমুসলিম দেশের বা তাবেদার মুসলিম সরকারের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন তাদের বিবেক যেন জাহেলী কবির ঘোড়ার চেয়েও সস্তা, যা ভাড়ায়ও খাটে, আবার বিক্রিও হয়।
প্রাচ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও বন্ধনের বৈশিষ্ট্য এই ছিলো যে, তার বুনিয়াদ কখনো বস্ত্তগত স্বার্থের উপর হতো না, বরং ইখলাছ, আন্তরিকতা, আত্মিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উপর হতো। প্রবৃত্তি ও আত্মস্বার্থের কালিমা তাতে খুব কমই থাকতো। এর ফলে সম্পর্ক ও বন্ধন এমন নিবিড় হতো এবং তার শেকড় হৃদয় ও আত্মার এত গভীরে প্রোথিত হতো যার কোন বস্ত্তগত ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তো এমন ছিলো যার তুলনা এ যুগের পিতা-পুত্রেও পাওয়া যায় না। একটি ঘটনাই শুধু বলি, হিন্দুস্তানের সুপ্রসিদ্ধ আলিম দরসে নিযামীর প্রবর্তক মোল্লা নিযামুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ শুনে তার ছাত্র সৈয়দ কামালুদ্দীন আযীমাবাদী শোকাঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন, আর অন্য ছাত্র সৈয়দ যরীফ আযীমাবাদী কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেলেন। পরে জানা গেলো, উস্তাদের মৃত্যুসংবাদ ছিলো ভুল। হয়ত এ যুগের মনমানস এমন ঘটনার সত্যতা হযম করতে চাইবে না, কিন্তু যিনি প্রাচ্যের স্বভাব ও মানসিকতা সম্পর্কে জ্ঞাত এবং উস্তাদ-ছাত্রের মুহববত সম্পর্কে অবগত তার জন্য এখানে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
নৈতিকতার ইতিহাস ও দর্শন সম্পর্কে ওয়াকিফহালমাত্রই জানেন, খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ইউরোপে একটি চিন্তাধারা আত্মপ্রকাশ করেছিলো এবং খৃস্টীয় উনিশ শতক পর্যন্ত নেতৃস্থানীয় বহু দার্শনিক ও নীতিশাস্ত্রবিদ এ চিন্তাধারার সমর্থক ছিলেন। ‘দেহ-সুখ’ই ছিলো তাদের বিশ্বাসের মূল কথা। তারা মনে করতেন, দেহের আনন্দ ও জৈবিক সুখই হচ্ছে সকল কর্ম ও চরিত্রের মানদ-। তারা বলতেন, ‘ইহ জীবনকে ভোগ করার সব সুবিধা লুফে নাও; সময়ের ছিটকে পড়া মুহূর্তগুলো হাতছাড়া করো না।’
এ চিন্তাধারা আবার দু’টি উপধারায় ভাগ হয়ে যায়। প্রথমটিকে বলা হতো আত্মস্বার্থবাদী, তাদের বক্তব্য ছিলো, ‘মানুষ ও তার প্রবৃত্তির মধ্যে কোন আড়াল ও প্রতিবন্ধক যেন না থাকে, যাতে প্রবৃত্তির যে কোন চাহিদা চাহিবামাত্র সে পূরণ করতে পারে এবং সুখ ও আনন্দের সর্বোচ্চ মাত্রা ভোগ করতে সক্ষম হয়।’ তাদের শেষ কথা ছিলো, ‘সুখ মানে প্রবৃত্তির যে কোন চাহিদা চরিতার্থ করা এবং জীবনের স্বাদ ও সাধ দু’হাতে কুড়িয়ে নেয়া।’
দ্বিতীয়টিকে বলা হতো, স্বার্থবাদী। তাদের বক্তব্য ছিলো, ‘এমন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা যাতে সর্বোচ্চসংখ্যক ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বাদ ও আনন্দ ভোগ করতে পারে।’ তাদের মতে নৈতিক কর্মকাণ্ডের কোনই মূল্য নেই, যদি না তা স্বজাতির গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষের জন্য আনন্দবিধানে সক্ষম হয়। তারা বলেন, ‘সুখ মানে কর্মযোগে মানুষের জন্য যাবতীয় স্বাদ ও আনন্দ নিশ্চিত করা এবং যাবতীয় দুঃখ-ব্যথা দূর করা।’
বলাবাহুল্য যে, নীতিশাস্ত্রীয় এই দর্শন ও চিন্তাধারার মূল চেতনাই হলো বস্ত্তবাদিতা, যা প্রাচ্যের স্বভাব, প্রকৃতি ও ঐশী বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্যের দর্শনে, চরিত্রে, সাহিত্যে, সভ্যতায় সর্বত্র তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে আছে।
পাশ্চাত্যের নীতিশাস্ত্রবিদগণ বলে আসছেন, ‘লাভ ও আনন্দলাভই নৈতিকতার মূল’, কিন্তু তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবসময় তারা বস্ত্তবাদিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কারণ নিজেদের বুদ্ধি ও যুক্তিকেই তারা মাপকাঠিরূপে গ্রহণ করেছেন, আর দুঃখজনকভাবে তা বস্ত্তবাদের খাতেই প্রবাহিত হয়ে চলেছিলো। ফলে কোন প্রকার বস্ত্ত-ঊর্ধ্ব লাভ বা উপকার কল্পনা করতেও তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি সক্ষম ছিলো না। এভাবে এমন এক নীতিশাস্ত্র ও নৈতিক দর্শন অস্তিত্ব লাভ করেছিলো যা ঐসব কোন বিষয় আলোচনায় আনতে প্রস্ত্তত ছিলো না, যেগুলোর স্থূল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লাভ বা উপকার নেই। এই বস্ত্ততান্ত্রিক চেতনা ধীরে ধীরে জীবনের সর্ব-অঙ্গনে বিস্তার লাভ করেছিলো। ফল এই হলো যে, পাশ্চাত্যের চিন্তা-বুদ্ধি বস্ত্তবাদ ও ভোগবাদের সবচে’ বড় উকীলরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। তাই চরিত্র ও নৈতিকতা যে পরিমাণ বস্ত্তগত উপকার বয়ে আনতো, সমাজ ও ব্যক্তিবর্গ তা দ্বারা যে পরিমাণ সুখ, স্বাদ, আনন্দ ও সচ্ছলতা লাভ করতো চিন্তা ও বুদ্ধির কাছে তা সেই পরিমাণে উত্তমতার সনদ লাভ করতো। এককথায় বস্ত্তগত লাভই হয়ে দাঁড়িয়েছিলো চরিত্র ও নৈতিকতার মানদ- এবং ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণকারী। বস্ত্তর মানদণ্ড যে চরিত্র ও নৈতিকতার কোন মূল্য নেই, প্রাচীন পরিভাষায় তার ধর্মীয় মূল্যই শুধু অবশিষ্ট ছিলো, পক্ষান্তরে হৃদয় ও মস্তিষ্কের উপর তার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ দিন দিন কমেই চলেছিলো এবং নীতিবাদী ও চরিত্রবাদী মানুষ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে অতীতের স্মৃতিরূপেই শুধু অস্তিত্ব বজায় রাখছিলো। যেমন সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ-মমতা, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস। এসকল নৈতিকতা ও মূল্যবোধের স্থান দখল করে নিয়েছিলো শিল্পশক্তি, উদ্ভাবন ও উৎপাদন এবং স্বদেশবাদ ও জাতীয়তাবাদ। এগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব এবং ধার ও ভার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিলো।
পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, আধুনিক সমাজ পারিবারিক বন্ধন, রক্তসম্পর্ক ও নৈতিক বিধিবিধানের কোন প্রয়োজনীয়তাই আর অনুভব করছে না। কারণ রাজনৈতিক, শিল্পনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখার ভিত্তিতে বিকল্প কিছু সামাজিক বিন্যাস ও গণব্যবস্থা সে উদ্ভাবন করে নিয়েছে। সুতরাং সমাজের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই যে, সন্তান পিতা-মাতার সঙ্গে বা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি কী আচরণ করছে, যদি তারা সেই নাগরিক সীমারেখা মেনে চলে যা সমাজ তার সদস্যদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। তদ্রূপ যদি কারো কোন আচরণ সমাজে গোলযোগ সৃষ্টি না করে এবং নির্ধারিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে এবং নাগরিকতার গতি ব্যাহত না হয় তাহলে সন্তানের পিতার অবাধ্য হওয়া, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বাস রক্ষা না করা, বা পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, এগুলো সমাজের কোন সমস্যা নয়।
পাশ্চাত্যের সভ্যতা ও সাহিত্যে বিগত শতাব্দীগুলোতে যে ক’টি শব্দের ব্যবহার সবচে’ বেশী হয়েছে এবং যেগুলোর মধ্যে ইউরোপ এখনো সবচে’ আকর্ষণ অনুভব করে সেগুলোর মধ্যে একটি হলো স্বভাব ও ফিতরত। তবে যে সকল ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হয় তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ফিতরত ও স্বভাব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পশুগত স্বভাব, যা সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম-কোমল অনুভূতি, বিবেক ও নৈতিকতা এবং বিশুদ্ধ হৃদয় ও বিশুদ্ধ মস্তিষ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং যা যে কোন বন্ধন ও সীমারেখাকে ভয় করে। এই পশুগত স্বভাবের একটাই শুধু দাবী, পানাহার করো, ভোগ করো এবং মুক্ত থাকো। অধিকার ও মানবিক দায়দায়িত্ব বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব তার কাছে নেই। উনিশ শতকে মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে যে গবেষণা করা হয়েছে এবং যার অভ্রান্ততা সাধারণভাবে মেনে নেয়া হয়েছে, (অর্থাৎ ডারউইনের ভ্রান্ত বিবর্তনবাদ) তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং চরিত্র ও নৈতিকতার উপর তার অনুভূত ও অননুভূত প্রভাব পড়েছে।
পরবর্তীকালে ইউরোপে শুরু হলো যন্ত্রযুগ। তখন মানুষ সম্পর্কে মানুষের চিন্তা-ধারণা হয়ে গেলো সম্পূর্ণ বস্ত্তগত ও পদার্থগত। পশুগত ধারণায় মানুষের পরিচয়সত্তায় যে সামান্য প্রাণ ও সজীবতা ছিলো বস্ত্তগত ধারণায় তাও বিলুপ্ত হয়ে গেলো। ইউরোপিয়ান নও মুসলিম মুহম্মদ আসাদ ইউরোপের এই নৈতিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। যদি প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক আধিপত্য এভাবেই বহাল থাকে, আর স্বয়ং ইউরোপে বড় কোন বিপস্নব না আসে তাহলে আজ পাশ্চাত্য সম্পর্কে যা কিছু বলা হচ্ছে আগামীকাল প্রাচ্য সম্পর্কেও তা সঠিক বলে মনে হবে, যার আভাস এখনই দেখা যাচ্ছে। জীবনের সকল অঙ্গনের মত প্রাচ্যের নীতি ও নৈতিকতাও এখন পাশ্চাত্যের ছাঁচে গড়ে উঠছে। সমাজের যে সকল শ্রেণী পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা দ্বারা পুরোপুরি প্রভাবিত তাদের চরিত্র ও নৈতিকতা পাশ্চাত্যের চরিত্র-দর্শনের সর্বোত্তম প্রতিবিম্বরূপে এখনই পরিগণিত হতে পারে। মুহম্মদ আসাদ বলেন-
‘(ইউরোপে) মানুষের এমন একটি শ্রেণী তৈরী হয়ে গেছে যাদের চরিত্র ও নৈতিকতা কার্যকর উপযোগ- বাদের প্রশ্নের ভিতরে ঘোরপাক খাচ্ছে। ফলে তাদের কাছে ভালো-মন্দের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হলো বস্ত্তগত সফলতা। পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবন বর্তমানে যে গভীর পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে তাতে নতুন চারিত্রিক উপযোগবাদ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। সমাজের বস্ত্তগত উপকারের উপর সরাসরি প্রভাবক গুণসমূহ, যেমন শিল্পযোগ্যতা, স্বদেশপূজা ও জাতীয়তাবাদী আবেগ, এগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং অস্বাভাবিক অতিশয়তার সঙ্গে। পক্ষান্তরে যে সকল গুণের এখনো পর্যন্ত শুধু নৈতিক মূল্য ছিলো, যেমন পিতৃস্নেহ, দাম্পত্য বিশ্বস্ততা, তা খুব দ্রুত গুরুতব হারাতে চলেছে। কেননা সমাজে এগুলোর তেমন কোন বস্ত্তগত উপকার নেই। পারিবারিক বন্ধনের দৃঢ়তাকেই পাশ্চাত্যে একসময় গোত্র ও পরিবারের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য মনে করা হতো, কিন্তু এখন আধুনিক পাশ্চাত্যসমাজে তার স্থান গ্রহণ করে নিয়েছে নতুন সামাজিক বিন্যাস, মৌলিকভাবে যা শুধু শিল্পনির্ভর। এ বিন্যাস খুব দ্রুত নির্ভেজাল যান্ত্রিক রূপরেখার উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে পিতার সঙ্গে সন্তানের আচরণ কোন সামাজিক গুরুত্ব বহন করে না, যতক্ষণ না তা সমাজনির্ধারিত সভ্যতা-ভদ্রতার সাধারণ সীমারেখার ভিতরে থাকে। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতা এবং পিতার প্রতি সন্তানের শ্রদ্ধা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্ক দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচেছ এবং কার্যত এমন একটি যান্ত্রিক সমাজ দ্বারা সেগুলো ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে যেখানে পারস্পরিক অধিকার রহিত করার প্রবণতা দেখা যায়, যার স্বাভাবিক ফল এই যে, পারিবারিক আত্মীয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকারসমূহও শেষ হয়ে যাচ্ছে।
(চলবে ইনশাআল্লাহ)