(৪)এতক্ষণ তুলে ধরলাম আমার আট ভাইবোনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আমি হলাম সবার ছোট। আমার জন্মতারিখ- আগেই বলেছি- ১৩৬২ হিজরীর ৫ই শাওয়াল। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর ইন্তিকালের বেদনাদায়ক ঘটনা এর প্রায় ... আগেই ঘটে গিয়েছিলো। ফলে তাঁকে দেখার, এমনকি তাঁর জীবদ্দশা লাভ করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার সব ভাইবোনের খোশকিসমত যে, হয় তারা হযরতকে দেখেছেন, নয়ত হযরত তাদের দেখেছেন। হয় তাদের দৃষ্টি হযরতের দর্শন-সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছে, নয়ত তাদের অস্তিত্ব হযরতের দৃষ্টির পবিত্রতা দ্বারা ধন্য হয়েছে। আমার কিসমতে না এটা ছিলো, না সেটা। তবে বলতে ইচ্ছে হয়,‘মায়খানেকা মাহরূম ভী মাহরূম নেহী’।কারণ একথা বলার সুযোগ আছে যে, আমার জন্মের আগে আমার নাম রেখে তবেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, আব্বাজানের দরখাস্ত ও আবেদন রক্ষা করে হযরত যখন আমার কোন বড় ভাইয়ের নাম নির্বাচন করতেন তখন তিনি একই শ্রুতিছন্দের কয়েকটি নাম বলতেন, যেন তা থেকে কোন একটি নাম রাখা হয়। এটা ছিলো হযরতের সূক্ষ্ম সৌজন্যবোধের পরিচায়ক। কারণ প্রত্যেক পিতার অন্তরে সন্তানের জন্য নাম নির্বাচনের যে একটা স্বভাবচাহিদা সুপ্ত থাকে, তাতে তার প্রতি কিছুটা প্রশ্রয় নিহিত রয়েছে।তো হযরতের নির্বাচিত কয়েকটি নাম, ওয়ালি, রাযি, যাকি-এর মধ্যে একটি নাম ছিলো তাক্বী, যা আমার আগে আর কোন ভাইয়ের জন্য রাখা হয়নি। মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে আব্বাজান রহ. হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর নির্বাচিত নাম -তালিকা থেকেই আমার জন্য এ নামটি রেখেছেন।আরেকটি কথা; হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ-এর ইনতিকালের পর আব্বাজান রহ.সাধারণত তাঁর প্রিয় উস্তায ও মুরুব্বি হযরত মিয়াঁ ছাহেব (হযত মাওলানা সৈয়দ আছগর হোসায়ন দেওবন্দী রহ.)-এর কাছ থেকে পরামর্শ ও নির্দেশনা গ্রহণ করতেন। তিনি ছিলেন কাশফ ও কারামাতের অধিকারী বুযুর্গ। এজন্য খুব সম্ভবত আমার নাম রাখার ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শেরও ভূমিকা ছিলো।আমার বড় ভাই তিনজনই দারুল উলূম দেওবন্দে পড়তেন। আমার তো তখন কায়দা বোগদাদীর পড়াও যথারীতি শুরু হয়নি। সুতরাং দারুল উলূম দেওবন্দে পড়ার সুযোগই আর থাকে কোথায়! তারপরো আমার খোশকিসমত এই যে, মাঝে মধ্যে আমার বড় ভাইদের সঙ্গে দারুল উলূমে প্রবেশ করা হতো। এ সুবাদে ঐ সময়ের দারুল উলূমের আবছা একটা ছায়া ও ছবি অবশ্যই অন্তরে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিলো।শৈশব ও মাতৃকোল যেন জীবনের বসন্ত-বাহার!আমরা যেখানে থাকতাম তার পিছনে পশ্চিম দিকে ছিলো আমাদের দাদা হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইয়াসীন রহ.-এর মূল বাড়ী। ওখানেই আমাদের দাদী ছাহেবা রহ. থাকতেন (যিনি হযরত গাঙ্গোহী রহ.এর বাই‘আত ছিলেন)। ওখানেই আমার আব্বাজানের শৈশব -সহ জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যাপিত হয়েছে।আমাদের এখান থেকে ঐ ঘর পর্যন্ত আসা যাওয়ার জন্য সুড়ঙ্সদৃশ একটা রাস্তা ছিলো, যেটাকে আমরা ‘নিমদরি’ (আধাদুয়ার) বলতাম। এই দাদা-ঘরের পিছনে আমাদের খান্দানেরই বিভিন্ন ঘর ছিলো। তার মাঝখান দিয়ে একটি চিকন গলিপথ ছিলো, যার শেষ মাথায় ছিলো অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত উন্মুক্ত ভূমি, আমাদের মুখে যার নাম ছিলো ‘চক’। আমাদের বয়সের সবার কাছে সেটা খেলাধূলার মাঠরূপে সুপরিচিত ছিলো। আমাদের ঐ সময়ের ছোট্ট কল্পনার জগতে সেটা আজকের কোন স্টেডিয়ামের চেয়ে কম ছিলো না। সারা মহল্লার সব ছেলেমেয়ে ওখানেই শৈশবের খেলাধূলার স্বভাবচাহিদা পূরা করতো। খেলাধূলাও ছিলো এমন যার সরঞ্জাম সংগ্রহ করার জন্য পয়সা খরচ করার যেমন দরকার ছিলো না তেমনি কোচ বা প্রশিক্ষকের সাহায্য গ্রহণেরও প্রয়োজন ছিলো না। জীবনের আর সব বিষয়ের মত শৈশবের খেলাধূলাও ছিলো স্বভাব ও ফিতরতের সঙ্গে নিবিড়।আমার বড় ভাইয়েরাও সাধারণত আছরের পর ঐ মাঠে ঐ সময়ের প্রচলিত কোন খেলা খেলতেন।আমার সম্পর্কে যদি বলি, আমি তখন ছিলাম তিন-চার বছরের এক অবুঝ বাচ্চা, যার পুরো দুনিয়া ঘর থেকে শুরু হয়ে ঐ চকের সীমানায় এসে শেষ হয়ে যেতো। ওখানে আমি নিজে খেলার চেয়ে অন্যদের খেলা দেখেই দিল খোশ করে নিতাম। নিজে খেলার সাধ ওসাধ্য দু’টোতেই আমার ঘাটতি ছিলো।আগে যেমন বলে এসেছি, আমার তিন ভাগ্নী ও এক ভাগ্নে বয়সে আমার কিছু বড় ছিলো, এই ধরুন এক থেকে তিন বছরের মধ্যে। তাই খান্দানের বাইরে বন্ধু তালাশ করার প্রয়োজনই ছিলো না। ঐ ভাগ্নি-ভাগ্নের সঙ্গেই ছিলো বন্ধুত্বের মত সম্পর্ক। শৈশবের নির্দোষ খেলাধূলার সম্পর্ক তাদের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিলো। ঐ সময়ের খেলাধূলার মধ্যে কানামাছি খেলাই ছিলো এমন যাআমরা নিজেদের বয়স হিসাবে খেলতে পারতাম। আর সেজন্য ঘরের অঙ্গনই ছিলো যথেষ্ট, ‘চক-স্টেডিয়াম’ ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো না। ডা-াগুলি জাতীয় খেলাও ছিলো আমাদের তখনকার সাধ্যের বাইরের জিনিস। এমনিতেও কখনো কোন খেলায় আমি তেমনদক্ষতা ও কুশলতা অর্জন করতে পারিনি।নয় ভাইবোনের মধ্যে আমি ছিলাম সবার ছোট। হয়ত এ কারণেই ছিলাম সবার আদরেরও। তো ঠিক জানি না, এটা কি সেই আদর-সোহাগেরই কারিশমা ছিলো, না আসলেই তাতে কিছু বাস্তবতাও ছিলো যে, সবার কাছে আমি ছিলাম বেশ ‘প্রতিভাবান’! মা-বাবা থেকে শুরু করে বোন-ভাই সবাই আমার ঐ ছোট্ট বয়সের বুদ্ধির তারিফ করতেন। আমার বুদ্ধির প্রমাণ হিসাবে যে সব ঘটনা পরিবারে আলোচিত হতো সেগুলো এখনো এমন স্পষ্ট মনে আছে, যেন আজকের ঘটনা, বা কালকের!!এর মধ্যে কিছু ঘটনা এখন কলমের মুখে আসার জন্য ব্যাকুল মনে হচ্ছে। হয়ত আপনিও তা শুনে ‘কল্যাণপূর্ণ বিনোদন’ লাভ করবেন; আপনার কাছেও হয়ত উপভোগ্য ও শিক্ষাযোগ্য মনে হবে। তো শুনুন-আমার আব্বাজান হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী ছাহিব, আল্লাহ তা‘আলা তাঁর উপর রহমত ও করুণার এবং রিযওয়ান ও সন্তুষ্টির ‘শবনম’ বর্ষণ করুন, তিনি ছিলেন দেওবন্দের মত প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুফতি। তদুপরি আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে ইলম ও জ্ঞানসমৃদ্ধির এমন উচ্চ মর্যাদা দ্বারা ভূষিত করেছিলেন যার খ্যাতি ও সুখ্যাতি সারা হিন্দুস্তানে বিস্তৃত ছিলো। তাঁর অসংখ্য প্রাণ-উৎসর্গী শিষ্য-ছাত্র যে কোন সেবা ও খেদমতের জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত ছিলো এবং এটাকে নিজেদের জন্য তারা অনেক বড় মর্যাদা ও সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতো। কিন্তু তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে এমন বিনয় ও সরলতা ছিলো যে, ঘরের সওদাপত্রের জন্য তিনি নিজেই বাজারে যেতেন। কখনো কখনো খরিদকরা জিনিস গামছার মধ্যেই বেঁধে নিয়ে আসতেন।তখন আমি এতটা উপযুক্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আব্বাজানের আঙুল ধরে বাজারে যেতে পারি। তো যখনই আব্বাজানের সঙ্গে বাজারে যাওয়া হতো ফেরার পথে তিনি আমাকে আমার পছন্দের কোন না কোন জিনিস নিয়ে দিতেন। টফি চকোলেটের সময় তো তখনো শুরু হয়নি। তাহলে আমাদের পছন্দের জিনিস কী ছিলো?! বুটভাজা এবং ভাজা ভুট্টার গুচ্ছ, মুড়ির মোয়া ও বরফমালাই (আইসক্রিমের স্থানীয় সংস্করণ)। এছাড়া ছিলো বাতাসা -সহ স্থানীয়ভাবে তৈরী কিছু মিঠাই। পরে যখন কিছুটা উন্নতি হলো তখন পাওয়া যেতো চকোলেটসদৃশ এক পয়সার ছোট আকারের মিঠাই, যা দেখতে ছিলো কমলার কোয়ার মত। একারণে সেটাকে আমরা বলতাম কমলামিঠাই। এখন মনে হয়, ঐ সময় বাচ্চাদের পছন্দের সব জিনিস ছিলো এমন যা স্বাস্থ্য-সম্মত এবং প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন। তাছাড়া সর্বত্র সুলভেই পাওয়া যেতো। বর্তমানে বাচ্চাদের খুশী করার জন্য যে সব অস্বাস্থ্যকর ও দামী জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছে সেগুলো তখন আমাদের কল্পনায়ও ছিলো না।যাই হোক, আব্বাজান রহ. যখন নিজের সঙ্গে আমাকে কোথাও নিয়ে যেতেন তখন ঐ সব পছন্দের কিছু না কিছু অবশ্যই নিয়ে দিতেন। ফলে আসা-যাওয়ার কষ্ট চুকে যেতো। আর বাজারভ্রমণের আনন্দ হতো বাড়তি পাওয়া।এখানে উল্লেখ করার মত বিষয় হলো, আব্বাজান রহ. যা কিছু নিয়ে দিতেন, নিজের পক্ষ হতে নিজের ইচ্ছায় দিতেন। বাচ্চারা নিজেদের পক্ষ হতে কোন বায়না-আব্দার জানাবে, সেটার রেওয়াজই ছিলো না (কান্নাকাটি করে আদায় করা তো দূরের কথা!)।তো একবার কী ঘটলো?! আব্বাজান রহ. বাজার থেকে আলু নিয়ে ঘরে ফিরছেন। আমি তার আঙুল ধরে সঙ্গে আছি। মনে আশা ছিলো, কিছু একটা পাবো। কিন্তু সেদিন কী হলো! আব্বা ভুলে গেলেন, সঙ্গে তাঁর বাচ্চাটি রয়েছে এবং তার মনেও কিছু আশা রয়েছে! যখন দেখলাম, আব্বাজান বাজার ছেড়ে ঐ গলিতে এসে পড়েছেন যেখানে বাচ্চাদের পছন্দের জিনিসগুলো নেই। হায়রে বাচ্চাদের বাচ্চা মন! তখন সত্যি সত্যি মনটা ভেঙ্গে গেলো এবং বুঝ হয়ে গেলো, এবার কিসমতে কিছু নেই! কারণ আগেই বলেছি, নিজের মুখে কিছু চাওয়ার, কিছু আব্দার-বায়না করার অভ্যাস ও রীতি কোনটাই ছিলো না। কিন্তু বাচ্চা মন কি এত সহজে আশা ছাড়তে চায়! মন চাচ্ছিলো, কোন না কোনভাবে আব্বার যেন মনে পড়ে যায়! একবার তো মুখে এসেই পড়েছিলো যে, বলি, আব্বাজান আপনি কিন্তু কিছু ভুলে যাচ্ছেন!এ দুই বিপরীতমুখী অবস্থার সমাধান আমার ঐ শৈশবীয় চিন্তায় এটাই এলো যে, কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলেই ফেললাম, ‘আব্বাজান, একটা আলুই না হয় আমার হাতে দিন!’আমার ‘নান্নামুন্না’ যবানে এ কথা শুনে আব্বাজানের ‘বে-সাখতা’ হাসি এসে গেলো। তিনি বড়দের আলুর পরিবর্তে বাচ্চাদের ‘আলু’ আমার হাতে তুলে দিলেন। ঘরে এসে সবাইকে তিনি আমার এ ঘটনা শুনালেন। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, সবাই হাসতে হাসতে শোনেন, আর শুনতে শুনতে হাসেন! পরে আমাদের ঘরের মহলে এটি বেশ ‘লতিফা’ ও কৌতুকরূপেই স্থায়ী হয়ে গিয়েছিলো।দেওবন্দে একটা সাপ্তাহিক বাজার বসতো প্রতি বুধবারে। এজন্য তার নাম ছিলো ‘বুধবাজার’; বুধবারের বাজার-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ঐ বাজারে আশপাশের গ্রাম্যরা বেচাকেনার জন্য আসতো। কিছু লোক নিজেদের সামগ্রী এনে বিক্রি করতো, অন্যরা নিজেদের প্রয়োজনের জিনিস খরিদ করতো। ঐ বাজারে সাধারণত গৃহস্থালি সামানপত্র সস্তা দামে পাওয়া যেতো।আব্বাজান রহ. একবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বাজারে গেলেন। ওখানে বাচ্চাদের পছন্দের জিনিস তেমন ছিলোও না, আর আব্বাজানেরও কোন কারণে মনে ছিলো না। বড়দের বিস্তৃত জীবনে চিন্তা কত বিক্ষিপ্ত থাকে তা ছোটদের তো বোঝার কথাও না। বড়দের চিন্তা যেখানে বাতাসের ঝাপটায় অস্থির, ছোটদের চিন্তা সেখানে ‘বাতাসায়’ স্থির! বাজারের শেষ দোকানটায় বাতাসা দেখতে পেয়ে আমি আর নিজেকে সংযমে রাখতে পারলাম না, বলে উঠলাম, আব্বাজী, বাতাসার দামটাই না হয় জিজ্ঞাসা করুন! উদ্দেশ্য ছিলো আব্বাজানকে তাঁর বিস্মৃত ‘দায়িত্ব’ মনে করিয়ে দেয়া। এটাও ছিলো আমাদের ঘরে আলোচনার বেশ একটা উপভোগ্য বিষয়!দেওবন্দের যে মহল্লায় আমাদের বসবাসছিলো তার নাম বড় ভাইদের মহল্লা। আসলে আমাদের সর্বশ্রদ্ধেয় দাদার সন্তানদের ‘বড় ভাই’ বলা হতো। সেই সুবাদে মহল্লাটিও এ নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলো। পূর্বমুখী ছিলো আমাদের ঘরের সদর দরওয়াজা। তার সামনেই ছিলো ঐ ছোট্ট সড়কটি, যা মুসলিম আবাদীকে হিন্দুদের বস্তি থেকে পৃথক করতো। অর্থাৎ আমাদের ঘরের বিপরীত দিকে ঐ সড়কটি পার হয়ে পুরো বস্তিটাই ছিলো হিন্দুদের। তবে তাদের সঙ্গে (মুসলিম) পড়শীদের ভালো সম্পর্কই ছিলো। আমাদের ঘরের সামনেই ঐ সড়কের উপর গমভাঙ্গানোর একটা কল ছিলো। আমরা বলতাম ইঞ্জিনঘর।মনে আছে, একবার ওখানে আগুন লেগেছিলো। আগুন নেভাতে যারা ছুটে গিয়েছিলো, আব্বাজান ছিলেন তাদের সবার আগে। দীর্ঘ সময় তিনি পানি বহন করে এনে আগুনে নিক্ষেপ করছিলেন। অমুসলিম প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচার করা ছিলো আমাদের আকাবিরীনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।আমার জন্য সেটি ছিলো ‘আকর্ষণীয়’ এক দৃশ্য। ঘরের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ঐ ‘তামাশা’ দেখার পর বড় ভাইবোনদের সামনে তোতলানো ভাষায় যখন ঐ দৃশ্যের বিবরণ দিলাম এবং অঙ্গভঙ্গি দ্বারা তার নকশা তুলে ধরলাম; এমনকি আগুন নেভানোর জন্য ইঞ্জিনের উপর একজনের চড়ার দৃশ্যটি চিত্রায়নের জন্য যখন ভাইবোনদের ঘাড়ে সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করলাম, তাদের জন্য তখন সেটা হলো বড়ই উপভোগ্য বিষয়। পরে তো এমন হলো যে, তারা ফরমায়েশ করতেন, ‘তাক্বী, ঐ দৃশ্যটা দেখাও তো দেখি! প্রায় ছয়বছর বয়স পর্যন্ত আমি তুতলিয়ে কথা বলতাম, উপভোগ্য লতীফা ও কৌতুকরূপে খান্দানে সেগুলোরও বেশ চর্চা ছিলো।হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.-এর বড় ছাহেবযাদা হযরত মাওলানা আযহার শাহ কায়ছার রহ.- যিনি দীর্ঘ দিন মাসিক দারুল উলূম দেওবন্দের সম্পাদক ছিলেন- আমাদের সবার বড় ভাই জনাব যাকী কায়ফী রহ.-এর বন্ধু ছিলেন। সেই সুবাদে আমাদের ঘরে তার বেশ আসা-যাওয়া ছিলো। আমার প্রতি তার ¯েœহ-মায়া ছিলো অনেক। ঘরে আমার আদুরে নাম ছিলো ‘তাক্কু’। তিনিও ঐ পারিবারিক আদুরে নামেই আমাকে ডাকতেন। অনেক সময় কোলে বসিয়ে তক্কু তক্কু করতেন, কিছুটা যেন চটানোর উদ্দেশ্যে।অন্যদিকে আমার কী হতো! তাঁর নাম ছিলো আযহার (যার অর্থ সবচে’ সমুজ্জ্বল; যদিও আমার তা জানা ছিলো না)। আমি তোতলানো জিহ্বায় তার নাম উচ্চারণ করতাম, যা বিকৃত হয়ে ‘আজহাল’ রূপ ধারণ করতো (অতিমুর্খ; যদিও এ অর্থ আমার বিলকুল জানা ছিলো না)। তিনি দরজায় এসে আওয়ায দিতেন, আমি বাইরে এসে তাকে দেখে বড় ভাইজানকে খবর দিতাম, ‘আজহাল ভাই এসেছেন’। তিনি আমার এই নির্দোষ তোতলানো উচ্চারণে খুব আনন্দ পেতেন।পাকিস্তানে এসে পরবর্তী জীবনে যখন আমার সম্পাদনায় মাসিক আলবালাগ আত্মপ্রকাশ করলো, প্রথম সংখ্যাটি আমি তার খেদমতে প্রেরণ করলাম। উত্তরে আমার নামে তিনি বড় সুন্দর একটি চিঠি লিখলেন, যা ছিলো বহু বছর পর আমার নামে তাঁর প্রথম পত্র। তিনি লিখলেন, ‘এখন তো আপনি মাওলানা মুহাম্মাদ তক্বী উছমানী। তবে আমার কাছে আপনি এখনো সেই তক্কু মিয়াঁ, যে কিনা আমাকে আজহাল বলে ডাকতো।’এমনকি পত্রের শেষে নিজের নামের স্থানে লিখলেন, ‘আপনার সেই আজহাল ভাই! আহ, শৈশবের দোষগুলোও কত নির্দোষ!!আমাদের ঘরে সাহিত্য ও কবিতার বেশ চর্চা ছিলো। আব্বাজান রহ.-এর কাব্যসমগ্র তো তাঁর ‘কাশকূল’-এ সঙ্কলিত হয়েছে। বড় ভাই জনাব যাকী কায়ফী রহ. তো ছিলেন যথারীতি কবি। তাঁর সুবাদে কতিপয় কবির আসা-যাওয়া হতে থাকতো আমাদের ঘরে। বড় দুই বোন যদিও কখনো কোন মাদরাসা বা স্কুলে পড়েননি, বরং শুধু গৃহশিক্ষা পর্যন্তই ছিলো তাদের...। কিন্তু তাঁদের কাব্যরুচি ও সাহিত্য-বোধ ছিলো পরিচ্ছন্ন ও উচ্চ মার্গীয়। মাঝে মধ্যে নিজেরাও কবিতা লিখতেন। এরূপ সন্তোষ-জনক পরিবেশের গুণে শৈশবের একেবারে ঐ কচি বয়সেও বেশ কিছু কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো, যা আমি তোতলানো জিহ্বায় উচ্চারণ করতাম, আর তা ঘরের সবার আনন্দের কারণ হতো। এটা ছিলো ঐ সময়ের কথা যখন ভারতবর্ষজুড়ে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার দাবানল জ্বলে উঠেছিলো।‘গড়মুক্তিশ্বর’ নামক স্থানে সেখানকার জনৈক কবি ঐ দাঙ্গার চোখে দেখা ঘটনার বড় হৃদয়বিদারক বিবরণ তুলে ধরেছিলেন তার এক কবিতায়, যা তখন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলো। ঐ কবিতার অংশবিশেষ তখন থেকেই আমার স্মৃতিতে গেঁথে রয়েছে-কত কী ঘটে গেলো সরকারের প্রশ্রয়ে- এই গঙ্গার তীরে!বস্তী জ্বলেছে, আগুনের ফুলকি উড়েছে-এই গঙ্গার তীরে!মায়ের চুম্বনে হত সিক্ত শতবার, ঐ কচি গালেই নরাধম বসাল খঞ্জর-এই গঙ্গার তীরে! ...চার ভাইয়ের মধ্যে বড়, আবার বোনদের মধ্যে সবার ছোট, যাকে আমরা ছোট আপা বলতাম, আল্লাহর ফযলে যিনি এখনো জীবদ্দশায় রয়েছেন, তিনি এই কবিতাটি উত্তম সুরে আমাকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। কবিতা ও তার সুর আমার এমনই মনে ধরেছিলো যে, যতক্ষণ না তাঁর মুখে সেই সুরে শুনতাম, ঘুম হতো না। পরে এমন হলো যে, ঐ কবিতাটি তিনি আমার জন্য ‘ঘুমপাড়ানি’রূপে ব্যবহার করতেন। পরবর্তী জীবনে তাঁকে সম্বোধন করে তাঁরই জন্য যে ‘প্রশস্তিকা’ রচনা করেছিলাম তার উদ্বোধনিকা ছিলো এই-ছোট আপা, তুমি শিরোনাম আমার এ কবিতার!এ সভার তুমি ভূষণ, তুমি অলঙ্কার!!প্রশস্তিকার শেষাংশে ঐ ঘুমপাড়ানির প্রতি ইঙ্গিত এসেছে এভাবে-ঘুমপাড়ানিতেও রেখেছো তুমি আলো শিক্ষার! বোন আমার, বন্ধু আমার, মা তুমি আমার!এছাড়া পুরো এলাকায় পাকিস্তান আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছিলো তার সমর্থনে অগ্নিঝরা বহু কবিতা রচিত হয়েছিলো। আমি কারো না কারো মুখে তা শুনে মুখস্থ করে নিতাম। তারপর আমার তোতলা উচ্চারণে খুব জোশের সঙ্গে তা আবৃত্তি করতাম। সবাই তাতে ‘মন হালকা’ করার উপায় লাভ করতো। মাওলানা আমের উছমানী রহ.-এর একটি কবিতা ঐ সময় বেশ প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। দু’টি পঙ্ক্তি দেখুন-কষ্টদুর্ভোগের করো যদি ভয়, নাম নিয়ো না আযাদীর!জেল-ফাঁসির নাই যদি সাহস, দায় নিয়ো না আযাদীর! ...এ জাতীয় উদ্দীপনাময় কবিতা কিছু না বুঝেই তোতলানো জিহ্বায় ‘নাস্তানাবুদ’ করে আমি আবৃত্তি করতাম, আর ঘরের সবাই তা ...!এটা ছিলো ঐ সময় যখন সারা হিন্দুস্তানে আযাদী আন্দোলন পূর্ণ যৌবনের অবস্থায় ছিলো, আর মুসলমানদের পক্ষ হতে পাকিস্তানের দাবী ক্রমশ জোরদার হচ্ছিলো। ফলে আমাদের ঘরের পূর্বদিকে যে ছোট সড়কটি, তাতেও মিছিলের পর মিছিল অতিক্রম করতো। আর মিছিলে যেহেতু সাধারণত কারো না কারো নামে যিন্দাবাদের ধ্বনি থাকতো, একারণে দূর থেকে মিছিলের শোরগোল শুনলেই তোতলানো ভাষায় আমি সবাইকে জানান দিতাম, জিন্দাহ বাদ আ-লাহে- হে! (অর্থাৎ যিন্দাবাদ আসছে)।এছাড়া মিছিলের বিভিন্ন শ্লোগান শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিলো। যেমন-‘বুকে গুলি খাবো, পাকিস্তান বানাবো’। ঐ সব শ্লোগান আমি যখন তোতলানো জিহ্বায় উচ্চারণ করতাম, ঘরের সবাই তা বেশ উপভোগ করতেন এবং শাবাস বলে উৎসাহ দিতেন।ফুফু আমাতুল হান্নান-এর ঘরোয়া মক্তবযে মহল্লায় আমাদের বাস ছিলো, তার মাথায়-আগেই বলেছি- একটি চক ছিলো। তো ঐ চকের কাছে আমাদের খান্দানের এক বিদূষী নারীর অবস্থান ছিলো। তাঁর নাম বিবি আমাতুল হান্নান। আমরা তাঁকে ‘ফুফ’ু ডাকতাম। কারণ সম্পর্কে তিনি আব্বাজানের বোন ছিলেন। তাঁর ঘরটি আসলে ঘর ছিলো না, ছিলো খান্দানের এবং দূর দূরের বাচ্চাদের এক আদর্শ দ্বীনী বিদ্যাঙ্গন! সেখানে কয়েক প্রজন্ম তাঁর কাছে শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলো। প্রধানত মেয়েদের, সেই সঙ্গে খুব ছোট ছেলেদের তিনি কোরআন নাযেরা পড়াতেন। নামে তো সেটা ছিলো নিছক কোরআনের নাযেরা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেহেশতি যেওরের মাধ্যমে মেয়েদের তিনি ঐ সব বিষয় শিক্ষা দিতেন যা ‘সারা জীবন’ কাজে লাগে। তিনি শুধু কিতাবের পাতা পড়িয়ে দিতেন না, আমলি তারবিয়াত ও বাস্তব দীক্ষাও দান করতেন। এই মকতবই ছিলো তাঁর দিন-রাতের মাশগালা এবং তাঁর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। এই মক্তবকে কেন্দ্র করেই তিনি শত শত ছেলে মেয়েকে ইনসানিয়াত ও মানবতা শিক্ষা দিয়েছেন এবং দ্বীন, ঈমান ও আখলাকের পথে পরিচালিত করেছেন।আমাদের বড় বোন থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত সবাই তাঁর কাছে পড়েছি।আমি তো তখন এ উপযুক্ত ছিলাম না যে, ঐ বিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্র হবো, তবে আম্মা-আব্বা আমাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে কায়দা বোগদাদি হাতে দিয়ে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। এভাবে কায়দা বোগদাদির প্রারম্ভ আমি ঐ ঘরোয়া মক্তবেই করেছিলাম। তাই না বোঝা অবস্থায়ও বুঝতাম, কী নিষ্ঠা ও মনপ্রাণ সঁপে দেয়া উদ্দীপনার সঙ্গে মুহতারামা আমাতুল হান্নান ছাহেবা তাঁর দ্বীনী তালীম-তারবিয়াতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। তাঁর আওয়াযও ছিলো বড় উদাত্ত ও গম্ভীর।এ সমস্ত কথা তো মনে আছেই। এছাড়াও বহু কথা স্মৃতির পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে যা হয়ত পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক, বা উপকারী মনে হবে না। তাই সেগুলো থাক।তখন আমার বয়স ছিলো কত? নিশ্চয়তার সঙ্গে তো বলতে পারি না, তবে সাড়ে চার বছরের চেয়ে অবশ্যই কম ছিলো। কেননা পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই আমরা দেওবন্দ থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য যাত্রা করেছিলাম।তবে আমাদের সবার বড় ভাই যাকী কায়ফী রহ.-এর বিবাহের ঘটনা বেশ মনে আছে, যা ১৯৪৬-এর শুরুর দিকে সম্পন্ন হয়েছিলো। ঐ সময় আমার বয়স নিশ্চিতভাবেই তিন বছর ছিলো, এর বেশী কিছুতেই নয়। সুতরাং যে সমস্ত কথা আমার স্মৃতিতে রয়েছে সেগুলো সব ঐ তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়সের কথা। আর এখন তো আমি অবাক হই যে, কালকের কথাও অনেক সময় মনে থাকে না; অথচ ঐ কচি বয়সের এ সমস্ত কথা এমনভাবে মনে আছে যেন সামনেই দেখতে পাচ্ছি।এর দ্বারা বোঝা যায়, শৈশবের কচি মনে যে সমস্ত কথার বা ঘটনার ছাপ পড়ে যায় তা কত দীর্ঘস্থায়ী এবং অমোছনীয় হয়ে থাকে। এজন্যই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়, ‘বাচ্চাদের সামনে শুধু ভালো কথা বলো, ভালো কিছু করো। মনে করো না যে, নাদান অবুঝ, আমাদের কথা বা কাজ তাদের উপর কী আর প্রভাব ফেলবে, এগুলো তো তাদের বুঝসমঝেরই ঊর্ধ্বে! মনেই বা থাকবে কত দিন!’হাঁ, একটা বিষয়,মনে হয় আমার জন্য বড় বঞ্চনার বিষয়, যার আফসোসও সবসময়দিলে ছিলো যে, তখনো দেওবন্দ ছিলো অতি উচ্চস্তরের ওলামা ও আউলিয়া কেরামের কেন্দ্রভূমি। কিন্তু ঐ ছোট বয়সে কারো সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার কথা আমার মনে নেই। এমন কিন্তু হতেই পারে না যে, আব্বাজান আমাকে তাঁদের সান্নিধ্যে নিয়ে যাননি।অবশ্য আম্মা-আব্বার সঙ্গে একবার থানাভোন যাওয়ার কথামনে আছে। আর সেটাই ছিলো স্মৃতিতে সংরক্ষিত প্রথম রেলসফর। তবে তখন কোন বোধ অনুভূতি ছিলো না যে, থানাভোন কী ও কেন? এভাবে থানাভোন যাওয়ার উদ্দেশ্যই বা কী?হযরত থানবী রহ.-এর পরে আব্বাজানের প্রিয়তম উস্তায ও মুরুব্বি হযরত মাওলানা সৈয়দ আছগার হোসায়ন ছাহেব (হযরত মিয়াঁ ছাহেব নামে প্রসিদ্ধ) জীবদ্দশায় ছিলেন। প্রবল ধারণা, আব্বাজান আমার ‘তাহনীক’ তাঁর দ্বারাই করিয়েছেন। এখানেও একই আফসোস্ যে, তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিতির কথা আমার স্মৃতিতে নেই। অনেক সব কথা মনে না রেখে যদি এই রকম কিছু স্মৃতি ধরে রাখতে পারতাম!পরবর্তীকালে একবার স্বপ্নে তাঁর যিয়ারত হয়েছিলো। তখন তাঁর যে ‘হুলিয়া’ ও চেহারাছূরত দেখেছি, ভাই বোনদের বলার পর তাঁরা সত্যায়ন করেছেন যে, এটা হযরতেরই হুলিয়া ছিলো। একই ভাবে শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ হোসায়ন আহমদ মদনী রহ. এবং শায়খুল আদব হযরত মাওলানা ই‘যায আলী রহ.-এর মত মহান আকাবির তখনো দেওবন্দে বিদ্যমান ছিলেন এবং বিশ্বাস করি, আব্বাজান আমাকে তাঁদের সান্নিধ্যে নিয়েছিলেন, কিন্তু আমার কাছে তার কোন স্মৃতি নেই! নেই তো নেই!!এরই মধ্যে ১৩৬৬ হি. ২৭শে রামাযান জুমু‘আতুল বিদা-এর বরকতপূর্ণ রাতে (১৪ই আগস্ট ১৯৪৭) পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে এবং ইসলামের নামে মুসলমানদের একটি আযাদ ভূখ-ের প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়। আমার বয়স তখন চারবছর কম আটদিন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিশেষ দিনটি তো বিশেষভাবে মনে নেই, তবে এতটুকু অবশ্যই মনে পড়ে যে, ঘরে বরাবর ‘পাকিস্তান’-এর আলোচনা ছিলো। ফলে আমার শৈশবের চিন্তায় এমন কিছু একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, বড় ও সুন্দর কোন বালাখানা তৈয়ার হয়েছে, যেখানে বড় বড় কামরা রয়েছে, আর দেয়ালে দেয়ালে চাঁদ-তারার আকর্ষণীয় সাজ-সজ্জা রয়েছে!যেই না পাকিস্তান হলো, অমনি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো। পূর্বপাঞ্জাবে নিরস্ত্র অসহায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর কৃপাণহাতে শিখেরা উন্মত্ত উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোমহর্ষক যুলুম নির্যাতনের যেন এক কেয়ামত শুরু হয়ে গেলো। ইউপির জেলা সাহারানপুর ছিলো পূর্বপাঞ্জাবের একেবারে লাগোয়া, এ কারণে এ অঞ্চলে শিখদের যথেষ্ট আবাদি ছিলো। আর দেওবন্দ ছিলো সাহারানপুরেরই একটি কছবা। ফলে শিখদের যুলুম-নির্যাতনের তা-ব আমাদের এলাকায়ও পৌঁছে গেলো। হিন্দুরা দাঙ্গাবাজ শিখদের আশ্রয়, প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছিলো। হিন্দুদেরও আগ্রাসী ও হিংসাত্মক মিছিল বের হতো, আর তাতে ‘রক্ত চাই, কল্লা চাই’জাতীয় ভয়ঙ্কর শ্লোগান শোনা যেতো। আমাদের মহল্লারপূর্বদিকে হিন্দুপাড়া নামে পরিচিত হিন্দুদের বস্তি ও বসতি যেহেতু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো সেহেতু প্রতিরাতেই এধরনের গুজব ‘টগবগ’ করতো যে, আজ রাতে শিখ-হিন্দুদের হামলা হবে। বলতে তো সহজই মনে হলো, কিন্তু এসব গুজব মুসলমানদের মধ্যে, বিশেষ করে নারী-শিশু ও বৃদ্ধ মাযূর মানুষগুলোর মধ্যে কেমন ভীতি ও ত্রাস সৃষ্টি করতো তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।তো সম্ভাব্য বিপদের কথা চিন্তা করে মহল্লার যুবকদল বিভিন্ন মোর্চা ও অবস্থানে পালাক্রমে সারারাত পাহারা দিতো।এরূপ বিভীষিকাময় পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আমার শৈশবীয় চিন্তায় বিশেষ করে শিখদের সম্পর্কে রক্তপিপাসু দানবের মূর্তি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিলো, যারা দেখামাত্রা মুসলমানদের কতল করে, আর কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে যদি আমার ঐ সময়ের একটি ঘটনা বলি। কী কারণে যেন ঘরের সবার উপর আমি, যাকে বলে, বিলকুল ‘নারায’ হয়ে গেলাম! ইচ্ছে হলো, সবাইকে আচ্ছা রকম জব্দ করি, আর বুঝিয়ে দিই, আমার নারায হওয়া এত হালকা বিষয় না! তা কী করা যায়! হঠাৎ করেই বুদ্ধিটা মাথায় এলো। হাঁ, এভাবেই সবাইকে জব্দ করা যায়! কাউকে কিচ্ছু না বলে রাতে ঘরের পূর্বদিকের দরজার কাছে এক কোণায় গিয়ে গুটিশুটি শুয়ে থাকলাম। ঐ কোণাটা আমার বুদ্ধিতে দু’টি কারণে খুব খতরনাক ছিলো। এক তো ওখানে লাকড়ীর স্তূপ ছিলো, যেখান থেকে মাঝে মধ্যেই বিচ্ছু বের হতো। দ্বিতীয়ত- এবং সেটা ছিলো ভয়ানক- ঐ দরজা খুললেই দেখা যেতো হিন্দুপাড়ার সড়কটি, দিন-রাত যেখানে শিখ-হিন্দুদের মিছিল-শ্লোগান চলতো। ওদিক থেকেই তাদের হামলার সবচে’ বেশী খতরা ছিলো।তো আমি আমার বুঝমত এ দু’টি বিরাট বিপদ-ঝুঁকির মুখোমুখি হয়ে ঘরের সবাইকে জানান দিতে চাইলাম, তাদের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে আমি এরূপ বিপজ্জনক প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছি।তো অনেক তালাশ করার পর যখন আমাকে ওখানে পাওয়া গেলো, সবাই তখন এমন জব্দ হলো যে, আমার তেজ আরো বেড়ে গেলো। ভাই-বোন একের পর এক আসে, আর আদরে সোহাগে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাকে ঘরে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। আমার ‘তুতলি’ মুখে একই কথা, ‘ছিচ্চু আও, আর বিচ্ছু আও, আমি এখানেই ‘পলে’ থাকবো।(ছিচ্চু হচ্ছে তখন আমার মুখে শিখ-এর তোতলা উচ্চারণ)আমার এই সঙ্গীন প্রতিবাদ যখন ভাই-বোন কেউ সাঙ্গ করতে পারলো না তখন আব্বাজানকে জানাতে হলো, আর তিনি এসে আমাকে কোলে নিলেন, আদর করলেন এবং ঘরে নিয়ে গেলেন। আমিও নরম হলাম। বলাবাহুল্য, আমার দাবী-আব্দার সবই তারপর মেনে নেয়া হয়েছিলো।আসলে বড়দের উপর বাচ্চাদের যা কিছু শোধ-প্রতিশোধ, বিশেষ করে মা-বাবার উপর, তার একমাত্র ভিত্তি হলো, তাদের আদর-¯েœহ ও মায়া-মমতার দুর্বলতা।(ইনশাআল্লাহ চলবে)
হযরত মাওলানা তাক্বী উছমানী মু. তাঁর মহান পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী’ রহ. সম্পর্কে লিখেছেন- ‘তাঁর জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো ছালাতের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা। যারা তাকে নামায পড়তে দেখেছেন তারা অবশ্যই বলবেন, নামায আরো দেখেছি, তবে এমন নয়! নামাযের মধ্যে তাঁর সর্বসত্তায় বিনয় ও দীনতা, ভীতি ও খাশয়াত, একাগ্রতা ও ফানাইয়্যাত এবং আত্মসমর্পিতি ও ইনাবাতের এমন ভাব ও কায়ফ বিরাজ করতো যে, তার নমুনা খুব কমই কোথাও পাওয়া যেতো। আমাদের মত রুচি ও অনুভূতিবঞ্চিত মানুষের পক্ষে তো এসকল উচ্চ মার্গীয় ভাব ও আচ্ছন্নতার সামান্য উপলব্ধিও কঠিন, বরং প্রায় অসম্ভব।আমাদের তো অভ্যাস এই যে, যখনই কোন ‘গুরুত্বপূর্ণ’ কাজ সামনে আসে চিন্তা ছাড়াই বলে ফেলি, নামায থেকে ফারেগ হয়ে নেই, তারপর এ কাজটা করবো। একদিন তিনি এ মন্তব্য শুনে তিরস্কারের সুরে বললেন, আরে ভাই, নামায তো ফারেগ হয়ে যাওয়া মত বিষয় না! নামায থেকে ফারেগ হওয়ার চিন্তা করা উচিত না, বরং অন্যান্য কাজ থেকে ফারেগ হয়ে যথাসময়ে নামাযের প্রতি মনোযোগী হওয়া কর্তব্য। তারপর তিনি সেই আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যা দিন-রাত আমরা পড়তে থাকি। আল্লাহ তাঁর পেয়ারা হাবীব ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب
দারুল উলূম করাচি বর্তমানে সত্তর একর আয়তনের বিশাল ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি দ্বীনী বিদ্যাঙ্গন! এর সূচনা হয়েছে ১৩৭০ হি. (১৯৫১), আমাদের প্রাণপ্রিয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফী রহ.-এর পবিত্র হাতে। শুরুতে কী ছিলো দারুল উলূম! করাচির নানকওয়াড়া এলাকার একটি জীর্ণ, নোংরা ইমারত। তিনি নিজের হাতে এই ইমারত পরিষ্কার করেছেন এবং একে কোন রকম বাস-উপযোগী করেছেন। কিন্ত তাঁর ত্যাগ ও কোরবানি এবং ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াতের বরকতে আজ তা এই শানদার রূপ লাভ করেছে! চরম থেকে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে যেভাবে তিনি নিজের অসুস্থতা ও রোগব্যাধির কোন পরোয়া না করে, নিজের আরাম-আয়েশ, এমনকি ন্যূনতম বিশ্রামেরও চিন্তা না করে যেভাবে ‘ত্যন, ম্যন, ধ্যন’ দারুল উলূমের পিছনে কোরবান করেছেন তার সাক্ষী তো এখনো রয়েছে। বস্তুত তাঁরই নির্জনরাতের আহাজারি, আর কর্মমুখর দিনের দৌড়ঝাঁপ-এর বরকতে আল্লাহ তা‘আলা দারুল উলূম থেকে দ্বীনের প্রত্যেক অঙ্গনে এত খেদমত নিয়েছেন। (তাক্বী উছমানী)
বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম
শিশু-কিশোর ও নবীনদের পত্রিকা
মাসিক আল-কলম-পুষ্প
সম্পাদক: আবু তাহের মিসবাহ
( এবং পুষ্পের লেখকবন্ধুরা )
[ একটি দারুল কলম প্রকাশনা ]
জী ব নে র পা থে য়
আমার স্মৃতি;কিছু সুখের,কিছু দুঃখের! শায়খুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তক্বী উছমানী (দা.)
বাংলা ইউনিকোডে টাইপ করুন। যেমন: কুরআন, তাওহীদ ইত্যাদি
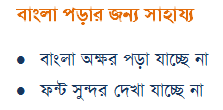
অন্যান্য লেখা
-
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
দরদী মালীর কথা শোনো: মাদানী নেছাব আকাবিরীনের চিন্তারই ফসল, তবে... -
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
কাশ্মীরের ই তিহাস-৩ -
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
আমার স্মৃতি; কিছু সুখের, কিছু দুঃখের!-৮ -
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
উছমানী সালতানাতের মযলূম খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ রহ. -৯ -
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
দেশ ও সমাজের দিনলিপি (ধারাবাহিক) -
রবিউছ ছানী ১৪৪৫ হিঃ
গীবত থেকে তাওবা করার পদ্ধতি -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
দরদী মালীর কথা শোন: আমার কিছু কষ্টের কথা! -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
কিতাবের পাতা এবং জীবনের পাতা -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
কা শ্মী রে র ই তি হা স -২ -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
দেশ ও সমাজের দিনলিপি (ধারাবাহিক) -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
পাশবিকতা ও প্রতিবাদ -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
আমার স্মৃতি; কিছু সুখের, কিছু দুঃখের! - ৭ -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
উছমানী সালতানাতের মযলূম খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ রহ. -৮ -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
অন্তরের স্বভাবপ্রতিক্রিয়া এবং করণীয়। -
মুহাররম ১৪৪৫ হিঃ
ফুলের প্রতি কৃতজ্ঞতা