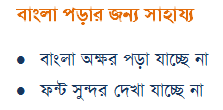আমার আকুতি ছিলো, কিন্তু ...!!
ধারাবাহিক
নানীর দাম্পত্য জীবন ছিলো মাত্র চৌদ্দবছরের, আর মৃত্যু পর্যন্ত বৈধব্যের জীবন ছিলো সুদীর্ঘ ঊনষাট বছরের। যখন থেকে নানীকে দেখেছি বুঝের বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্তই তো দেখেছি করুণ, কোমল ও স্নিগ্ধ একটি বিষণ তার মধ্যেই দেখেছি। এমনকি ঘরে যখন খুশি ও আনন্দের কোন উপলক্ষ হতো তখনো নানীর মুখম-লে সেই বিষণ তাটি বিরাজ করতো। সবার সঙ্গে খুশিতে শরীক হতেন, হাসতেন, এমনকি আমাদের হাসাতেন, আনন্দ দিতেন। তবে, তাতেও থাকতো বিষণœতার করুণ কোমল ও স্নিগ্ধ আবরণ তখন মনে হতো!
‘নানীর সব আছে, সবাই আছে, তবু যেন কিছু নেই, তবু যেন কেউ নেই।’
জীবনে কাকে বলে স্বামীর অভাব, মাথার উপর যদি স্বামীর ‘রক্ষাছায়া’ না থাকে তখন সবকিছুর মধ্যে থেকেও একজন বিধবার জীবন কতটা রিক্ত ও নিঃস্ব হতে পারে এবং হতে পারে কতটা বেদনার, আমি একজন পুরুষ তা কী করে বোঝবো! তবে একটা কথা বুঝেছি, বৈধব্যের কঠিন জীবনেও নানীর অনন্যসাধারণ মাতৃরূপ থেকে
নারীর জীবনে স্বামী ‘সব’ হলেও, সন্তান হলো ‘সর্বস্ব’।
তাই ‘এমন’ স্বামী ও তাঁর নিরাপত্তার ছায়া হারিয়েও শুধু সন্তানের মুখ চেয়ে, বিশেষ করে দুধের শিশুকে বুকে নিয়ে নানী বেঁচে থেকেছেন; বেঁচে থাকতে পেরেছেন। শুধু আমার নানী কেন, সংসারের প্রায় প্রতিটি ‘বিধবা মা’-এর ক্ষেত্রেই এটা সত্য, এ যুগে এবং সবযুগে; এ দেশে এবং সবদেশে।
আম্মার কাছে শুনেছি, দুধের শিশুকে কোলে নিয়ে নানী যখন... তখন বুকে দুধের ঝরণা এবং চোখে অশ্রুর ফোয়ারা, দু’টোরই প্রবাহ একসঙ্গে হতো, নীরবে, নিঃসব্দে; হৃদয়ের গভীরে আনন্দ ও বেদনা, যাকে বলে মাখামাখি হয়ে।
আমার আম্মা ছিলেন তখনকার অল্প বয়সেও যথেষ্ট বুদ্ধিমতী এবং কোমল ও সংবেদনশীল হৃদয়েরমেয়ে। তাই মেয়ে হয়েও এবং স্ত্রীজীবনের পরিচিত কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মায়ের প্রতি তাঁর যেন ছিলো আশ্চর্য একটি ‘মাতৃমমতা’, যা চোখের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তরের দৃষ্টি একত্র হলেই শুধু অনুভব করা যায়, তবে শব্দের অবয়বে তা প্রকাশ করা যায় না কিছুতেই। আমার আম্মাকে, বার্ধক্যের পূর্ব থেকে যিনি এখন বার্ধক্যের পশ্চিমে উপনীত, চিরকাল আমার আম্মাকে তাঁর আম্মার প্রতি ‘ফুলের পাপড়ীর মত’ এমন স্নিগ্ধ কোমল মাতৃমমতার জ্যোতির্ময় রূপেই দেখেছি। মায়ের প্রতি মেয়েহৃদয়ের এই যে আশ্চর্য মাতৃমমতা, এর কল্যাণেই নানীর বৈধব্যের সব কষ্ট ও বেদনা, আম্মা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। দুধের শিশুকে কোলে নিয়ে নানী বসে আছেন! বসে আছেন তো বসেই আছেন!
চোখের দৃষ্টি বিষণ ছলছল! হয়ত কোন দিকে তাকিয়ে আছেন, তবে সেই দৃষ্টিতে বর্তমানের, বা ভবিষ্যতের কিছু দেখা যায় না; দেখা যায় শুধু হারিয়ে যাওয়া অতীতের কিছু কষ্টের, কিছু আনন্দের দৃশ্য! হয়ত কিছু ভাবছেন, তবে সে ভাবনা বর্তমান ও ভবিষ্যতকে অবলম্বন করে নয়, শধু অতীতের আনন্দ-বেদনাকে অবলম্বন করে। নানীর সেই ধ্যানমগ্ন রূপটি দেখে আম্মা ঠিকই বুঝতেন, দূরের কোন্ অচীন জগতে তাঁর মা এখন বিচরণ করছেন, আর তাঁর বুকের ভিতরে কিসের ঝড় বইছে! আম্মা তখন নানীর পাশে গিয়ে শরীরের উত্তাপ দিয়ে মায়ের অন্তরে নিজের হৃদয়ের উত্তাপ-উষ্ণতাটুকু প্রবাহিত করার নীরব প্রয়াস! মেয়ের হৃদয়ের মমতার উত্তাপ পেয়ে নানী তখন একেবারে যেন বিগলিত হতেন! অনেক কষ্টে ধরে রাখা অশ্রু যেন বাঁধ ভেঙ্গে নেমে আসতো!
প্রথম সন্তান ছেলে এবং মেয়ে হওয়ার মধ্যে এখানেই বুঝি পার্থক্য! প্রথমটায় আশ্রয় ও নিরাপত্তা বেশী হলেও দ্বিতীয়টিতে তাপ ও উত্তাপ এবং মমতার উষ্ণতা অনেক বেশী। এটা আমি অত্যন্ত জীবন্ত রূপে অনুভব করেছি যখন মা ও মামার মাঝখানে নানীকে জীবনের ‘নিঃসঙ্গ দিন-রাত ও সকাল-সন্ধ্যা পার করতে দেখেছি। আর যখন দেখেছি, নানী দাঁড়াতেন। কিচ্ছু না বলে; সান্ত¡নার একটা শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ না করে! শুধু পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন একেবারে সংলগ্ন হয়ে; যেন শরীরের উত্তাপ দিয়ে মায়ের অন্তরে নিজের হৃদয়ের উত্তাপ-উষ্ণতাটুকু প্রবাহিত করার নীরব প্রয়াস! মেয়ের হৃদয়ের মমতার উত্তাপ পেয়ে নানী তখন একেবারে যেন বিগলিত হতেন! অনেক কষ্টে ধরে রাখা অশ্রু যেন বাঁধ ভেঙ্গে নেমে আসতো!
প্রথম সন্তান ছেলে এবং মেয়ে হওয়ার মধ্যে এখানেই বুঝি পার্থক্য! প্রথমটায় আশ্রয় ও নিরাপত্তা বেশী হলেও দ্বিতীয়টিতে তাপ ও উত্তাপ এবং মমতার উষ্ণতা অনেক বেশী। এটা আমি অত্যন্ত জীবন্ত রূপে অনুভব করেছি যখন মা ও মামার মাঝখানে নানীকে জীবনের ‘নিঃসঙ্গ দিন-রাত ও সকাল-সন্ধ্যা পার করতে দেখেছি। আর যখন দেখেছি, নানী পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যাওয়া সূর্যটার দিকে তাকিয়ে আছেন, পাশে শুধু তাঁর বড় মেয়ে, আমার মা! আমাদের আম্মা!!
***
নানার ইনতিকাল হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, ১৯৫৪ সালে। এখনকার চেয়ে তখন অবস্থা কত ভিন্ন ছিলো! তবু মায়ের কাছে শুনেছি, হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে নানা বলতেন, আল্লাহ্ শত্রুকেও যেন হাসপাতালে না আনে।
নানার যখন ইন্তিকাল হলো, নানী তখন সন্তানদের নিয়ে ঢাকা শহরে অথৈ সাগরে; না কোন আশ্রয়, না কোন সম্বল। না কোন আশ^স, না কোন সান্ত¡না! ছিলো শুধু অদৃশ্যের প্রতি পরম নির্ভরতা, যা তিনি অর্জন করেছেন স্বামীর এতদিনের সঙ্গ ও সান্নিধ্য থেকে। নানার ‘জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় আলোকিত’ জীবন থেকে।
নানা ছিলেন পুরোনো ঢাকার নাজিরা বাজার এলাকায় মসজিদের ইমাম! এমন ইমাম, যার প্রতি ছিলো সবার অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধা। তাঁর সঙ্গে যাদের ছিলো পাঁচ ওয়াক্তের পবিত্র বন্ধন এবং যাদের ছিলো শুধু বিবাহ-জানাযার সম্পর্ক তাদের সবার অভিন্ন বিশ্বাস ছিলো, ইমাম ছাহেব একজন ভালো মানুষ, পাক-পাকীযা ইনসান! আম্মার বিবাহ হলো নানার মৃত্যুর ঠিক পাঁচ দিনের মাথায়। আল্লাহ্ জানেন, কেমন বিবাহ ছিলো সেটি! এমনিতেই বিবাহ হচ্ছে জীবনের সবচে’ অনিশ্চয়তা -পূর্ণ বন্ধন-অনুষ্ঠান যা সম্পন্ন হয় বরের মুখের হাসি এবং কনের চোখের পানি, এ দু’য়ের মিশ্রণে! একটি মেয়ে দুরু দুরু বুকে বিবাহের বন্ধন গ্রহণ করে নিজের এবং মা-বাবার চোখের অশ্রুতে সিক্ত হয়ে। সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকে এটাই মানব-সভ্যতার পরম সত্য ও চরম বাস্তবতা। তবে সেই অশ্রুর মধ্যেও থাকে কিছু না কিছু আনন্দের মিশ্রণ এবং থাকে অজানা শঙ্কার মধ্যেও অধরা এক স্বপ্নের মৃদু কম্পন। কিন্তু আমার মা! আমাদের আম্মা! তাঁর চোখের পানিতে তখন কী ছিলো, জানতে বড় ইচ্ছে করতো আমার! যখনই জিজ্ঞাসা করেছি, আম্মা নীরব দৃষ্টিতে আমার দিকে শুধু তাকিয়ে থেকেছেন! সেই দৃষ্টি ছিলো এমনই বেদনাক্লিষ্ট যে, আমি কুণ্ঠিত হয়ে পড়তাম। এখন আর জিজ্ঞাসা করি না। তবে হৃদয়ের অনুভূতি থেকে যতটা উপলব্ধি করেছি, আম্মার জীবনে সেটা ছিলো বড় কঠিন দিন, যার মুখোমুখি তাঁকে হতে হয়েছে জীবনের অনিবার্য দাবী রক্ষা করার জন্য।
হাঁ, এখন মনে পড়েছে, একদিন আম্মা বলেছিলেন, কী যেন এক প্রসঙ্গে, ‘সবাই আমারে সাজায়, আর আমার খালি মনের মধ্যে ভাসে, আব্বারে খাটে কইরা আজীমপুর নিয়া গেছে! ...’
এটাই ছিলো আমার মায়ের বিবাহের ‘আনন্দরূপ’!
ঐ এলাকায় ছিলেন মরহূম মাজেদ সরদার। মসজিদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ইমাম ছাহেব মাত্র ইন্তিকাল করেছেন। তাঁরই বড় মেয়ের বিবাহ! তখনকার যুগে মানুষগুলো আসলেই ভালো ছিলেন; যথেষ্ট মানবিক ছিলেন! এখনকার চেয়ে ভালো তো অবশ্যই। আম্মার বিবাহের ‘আনন্দ-বেদনায়’ মহল্লার সবাই যেমন শরীক ছিলেন তেমনি মরহূম মাজেদ সরদার সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়েছিলেন। এখনো মাজেদ সরদারের প্রসঙ্গ এলে আম্মার অভিব্যক্তিতে কৃতজ্ঞতার উদ্ভাস দেখি। মরহূম মাজেদ সরদারকে শৈশবে (সম্ভত) আমি দেখেছি। তার মুখের ঢাকাইয়া কথা এখনো যেন কল্পনায় শুনি! আবারো বলতে ইচ্ছে করে, সবমিলিয়ে তিনি ভালো মানুষ ছিলেন, বিশেষ করে এখনকার বিচারে। আল্লাহ্ সবাইকে সব ভালো কাজের উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।
***
নানার জীবন সম্পর্কে আমার কিছু কথা, কিছু ভাবনা আশা করি পরে আসবে। এখানে শুধু একটি কথা; নানা লেখক ছিলেন; ভালো লিখতেন। চিন্তা ছিলো পরিচ্ছন্ন, ভাষা ছিলো পরিশীলিত। চকবাজারের এমদাদিয়ার মত অভিজাত প্রকাশক তাঁর বই প্রকাশ করতো। তবে অর্থের কাছে এসে তখনকার সব প্রকাশকেরই আভিজাত্য কিছুটা হলেও মলিন হয়ে যেতো। এমদাদিয়া এর ব্যতিক্রম ছিলো না। জীবনের শেষ দিকে সম্ভবত প্রকাশকদের অসদাচরণে অতিষ্ঠ হয়েই নানা নিজের বই নিজেই ছাপা শুরু করেছিলেন।
এখন আমরা যারা কলম ‘চালিয়ে’ কিছুটা হলেও অনুকূল ও নির্ভার জীবন যাপন করি তাদের বোঝার কথা নয়; কল্পনা করারও কথা নয় যে, তখন একজন লেখকের জীবন ও জীবিকা কতটা কষ্টের, বরং কতটা অসম্মানের ছিলো। নানার বড় মেয়ে, আমার আম্মার নিজের অভিজ্ঞতা, ‘সকালে আব্বা বের হতেন একথা বলে যে, লাইব্রেরী যাই, দেখি কিছু পয়সা পাওয়া যায় কি না! আম্মা, আর আমি বিকালে অপেক্ষায় থাকতাম। আব্বা যখন আসতেন, দূর থেকে আব্বার মুখ দেখেই বুঝতাম ...! আব্বা রাত জেগে লিখতেন সেই পয়সায় যখন বাজার হতো, নতুন কাপড় আসতো...!’
নিজের বই নিজে প্রকাশ করা, এটা ছিলো লেখকের জন্য বড় বিড়ম্বনার। কারণ কোন প্রকাশক লেখকের বই প্রকাশ করলে লেখক বঞ্চিত হতেন, আর লেখক যখন নিজে প্রকাশক হতেন তখন তিনি হতেন সর্বস্বান্ত। নানার ভাগ্যে সেটাই ঘটেছিলো। ‘হযরত খাদীজা’, ‘হযত ফাতেমা’ ও ‘নূরনবী’ বইগুলোর কথা আমারও মনে আছে। দেখেছি, আব্বার অক্লান্ত চেষ্টায় কিছু বই বিতরিত হওয়ার পরো আমাদের ঘরে বইয়ের স্তূপ ছিলো দীর্ঘ দিন ।
তো ঐ বইগুলো, আব্বা, যেখানে আব্বার মাথাগুঁজার ছোট্ট একটা ঠাঁই ছিলো সেখানে কোনরকম ঠাসাঠাসি করে রাখার ব্যবস্থা করলেন, আর নানী সন্তানদের নিয়ে চলে এলেন স্বামীর বাড়ী, দাউদকান্দির গৌরীপুরের বানিয়াপাড়া গ্রামে। সেখানে ভিটের উপর মোটামুটি ভদ্রস্থ একটা ঘর ছিলো, তবে জীবন ধারণের অবলম্বন হতে পারে, তেমন কিছু ভূমি ও সম্পদ ছিলো না। এভাবেই শুরু হলো সংসারের অথৈ সাগরে নানীর বৈধব্যের কঠিন জীবন পাড়ি দেয়ার সংগ্রাম!
হিন্দুসাহিত্যে বৈধব্যের উপমা হলো জ্বলন্ত চিতা’। আমাদের কলমে এ উপমার স্থান নেই। আমি কোন উপমা ছাড়াই শুধু বলতে পারি, খুব নীরবে, কাউকে বিশেষ কিছু বুঝতে না দিয়ে নানী তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করেছেন, আর কোন না কোনভাবে সন্তানদের আগলে রেখেছেন। যখন যা জুটাতে পেরেছেন, তদের মুখে তুলে দিয়েছেন। তাতে হয়ত ক্ষুধা দুর হতো না, তবে বেঁচে থাকার একটা উপায় হতো। নানীর এই কঠিন জীবনের পুরো সময়টার সাক্ষী ছিলেন আমার মা। মামা তো দুধের শিশু, তিনি জানবেন কী করে, জীবনের রোদ থেকে বিধবা মা তাঁর ছেঁড়া আঁচলটি দিয়ে বুকের মানিককে আড়াল করে রাখার প্রাণান্ত চেষ্টায় কেমন বিপর্যস্ত হচ্ছেন। ছোট খালাম্মা ছিলেন আসলেও ছোট, তিনি শুধু জানতেন, ক্ষুধা পেলে কাঁদতে হয়! তারপর যা কিছু যন্ত্রণা সেটা নানী নীরবে সয়ে যেতেন বুকের দীর্ঘশ্বাস এবং চোখের পানি অবলম্বন করে। বড় খালাম্মা বড় হলেও ছোটই ছিলেন। সামান্য কিছু বুঝলেও অনেক কিছুই ছিলো তাঁর বুঝের বাইরে।
তবে বড় খালাম্মার একটা কথা মনে পড়ে এখন, তিনি বলেছিলেন, ‘তোমার আম্মা, আমার বড় আপা আসলে তখন ছিলেন মায়ের মত। কিছু দিতে না পারার যে কষ্টে আম্মার বুকটা... বড় আপা সেইগুলা যদ্দুর পারতেন আমাদের দেয়ার চেষ্টা করতেন। ...
অর্থাৎ আর কিছু না হোক, এটুকু বোঝার এবং উপলব্ধি করা বয়স ও অনুভূতি তাঁর ছিলো।
বড় খালাম্মার জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার কিছু আগে এক ঈদের রাতে তাঁর সান্নিধ্যে কিছু সময় যাপন করার একটা উপলক্ষ তৈরী হয়েছিলো। মসজিদ থেকে আমাদের বাড়ী, মাঝখানে ছিলো বড় খালাম্মার ‘স্বামীর বাড়ী’। কিছু উপসর্গের কারণে ওখানে যাওয়া আমার জন্য যথেষ্ট বিড়ম্বনার কারণ ছিলো। তবু ই‘তিকাফ থেকে ফেরার পথে বড় খালাম্মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়ে বলেছিলেন, ‘ঈদের চান দেহি আমার ঘরেই আইয়া পড়লো!’
মানুষ যখন আসন্ন মৃত্যুর ‘ঘ্রাণ’ পায় তখন সম্ভবত জীবনের ফেলে আসা অতীতের প্রতি বেশী কাতর হয়ে পড়ে। বড় খালাম্মার মধ্যে ঐ রকম একটা অত্যন্ত কাতরতা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছি, যদিও অন্তর্নিহিত রহস্য তখন অনুধাবন করতে পারিনি। সেদিন তিনি অনেক কথা বলেছিলেন, নিজের মা সম্পর্কে, বড় আপা সম্পর্কে এবং ...!
এখন থাক সে প্রসঙ্গ। সুযোগ হলে আবার না হয় বলা যাবে।
এ বিষয়ে আমার শুধু একটা দৃশ্য একটু একটু মনে পড়ে। আম্মা নানীর বাড়ীতে এসেছেন দাদার বাড়ী থেকে, অর্থাৎ স্বামী বা শশুরবাড়ী থেকে। একটা সাবান, এককৌটা তেল, কিছু চুড়ি ফিতা, এজাতীয় আরো কিছু জিনিস সঙ্গে এনেছেন বড় যত করে কাপড়ে পেঁচিয়ে। সেগুলো একে একে খুলে বড় খালাম্মার হাতে তুলে দিচ্ছেন। এখন তো ভাবলেও চোখে পানি আসতে চায় যে, এতীম ছোট্ট ভাইটি, ছোট বোনদু’টি, আর বিধব মা, তাদের প্রতি কেমন ছিলো তখন আমার আম্মার মনের আকুতি! এখনো যেন চোখের সামনে ভাসে, মায়ের কোলে বসে আমি তাকিয়ে আছি অবাক চোখে চুড়ি-ফিতার দিকে! বড় খালাম্মাকে আনন্দ দেয়ার জন্য আম্মা চুড়িগুলোর রিণিঝিনি শোনাচ্ছেন!
এখন মনে নেই, কেঁদেছিলাম কি না, চুড়ি আছে, ফিতা আছে, অথচ আমার জন্য খেলনা নেই! হয়ত কেঁদেছি, কারণ খেলনার প্রতি আমরা দুর্বলতা ছিলো। হয়ত কাঁদিনি, কারণ, মা বলেন, সেই ছোট বয়সেও ‘অসময়ে’ কান্নাকাটি করে মাকে তেমন জ্বালাতন করিনি।
এখন চিন্তা করলে একটা বিষয় বুঝতে পারি, মায়ের তখনকার জীবনে আমি যতটা অংশ জুড়ে ছিলাম, আম্মার জীবনে তাঁর ভাই -বোন তার চেয়ে বেশী অংশ জুড়ে ছিলেন, যদি বলি, ভুল হবে না। হয়ত আম্মা ভাবতেন, তার সন্তানের জন্য তো বাবা আছেন এবং আছেন দাদা ও দাদী, কিন্তু তাঁর এতীম ভাই ও বোনদু’টির জন্য তো...!
তো বলছিলাম, কান্নার কথা তো এখন মনে নেই, তবে এটা মনে আছে বেশ স্পষ্ট, সামান্য চুড়ি আর ফিতা দিতে পেরে আমার মায়ের মুখে ছিলো এখন যেমন অনুভব হয় তৃপ্তির হাসি, আর সেটাকে ‘অসামান্য’ প্রাপ্তি মনে করে বড় খালাম্মার মুখে ছিলো কৃতজ্ঞতার হাসি!
শুরুর জীবনে আব্বার সঙ্গতি বলতে কিছুই ছিলো না, সামান্য তেলসাবান যাই দিতেন, আম্মা সেগুলো ছোট দু’টি বোনের জন্য বাঁচিয়ে রাখতেন। একদিন দাদী নাকি বলেছিলেন, আম্মার মাথার তেলহীন চুল দেখে...!
একজন শাশুড়ী তার পুত্রবধুকে শিক্ষার জন্য হলেও অনেক কিছু বলতে পারেন, আর কণ্ঠে সোহাগের সুর যেমন থাকতে পারে তেমনি থাকতে পারে শাসনের সুর। তবে হয়ত আম্মার তখনকার নিজস্ব অবস্থার প্রেক্ষিতে দাদীর কথাগুলো কষ্টের কারণ হয়েছিলো।
হায়, আমার সেদিনের দাদীআম্মা এখন কবরে শুয়ে আছেন! হায়, আমার দাদীর সেদিনের বালিকা পুত্রবধু, রোগে শোকে বিপর্যস্ত আমার আজকের আম্মা এখন শেষ ডাকের ইন্তিযারে আছেন!! জীবননদীর ¯স্রোতের টানে এভাবেই আমরা সবাই ভেসে চলেছি মহাসাগরের দিকে! সান্ত¡না এই যে, সেই মহাসাগর অনন্ত দয়া ও করুণার মহাসাগর!
আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী সবাইকে আল্লাহ্ মাগফিরাত নছীব করুন এবং জান্নাতে আ‘লা মাকাম দান করুন, আমীন।
***
দাদার বাড়ী থেকে নানীর বাড়ী ছিলো উত্তরপশ্চিম দিকে। প্রথম প্রথম আম্মা যখন দাদার বাড়ী আসতেন, একলা হলেই উত্তর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, মনে হতো আকাশের গায়ে যেন আম্মার ঘর দেখা যায়, আম্মাকেও দেখা যায়, আর দেখা যায় তিনটি ভাই- বোনের মেঘে আঁকা ছবি! উত্তরের আকাশ যখন ভার করতো, আম্মার বুকটা দুরু দুরু করতো। কী উপায় হবে আম্মার এবং ভাই-বোনদের, যদি ওখানে ঝড় হয়! মনে মনে কলেমা দু‘আ পড়তেন, ওখানে যেন ঝড় না হয়! সবাই যেন নিরাপদে থাকে।
মাঝে মাঝে সূর্যাস্তের সময় আম্মা দিগন্তে তাকিয়ে থাকতেন, আর ভাবতেন, আম্মা এখন কী করছেন। কুপি জ¦ালছেন! তেল আছে! তেল আনার পয়সা আছে! সাজেদা হয়ত নিজে অজু করে, বোনটিকে হাতমুখ ধুইয়ে ঘরে গিয়েছে। কোলের ছোট ভাইটি! এখন হাসছে, না কাঁদছে; নাকি চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে!
এভাবে কত কী যে ভাবতেন, আমার মা তার আম্মাকে নিয়ে, ভাই-বোনকে নিয়ে! কখনো কখনো নিজের অজান্তেই তাঁর চোখে পানি আসতো! কেউ আবার দেখে ফেলে কি না, তাই আঁচলে তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিতেন!
আব্বার জীবনের শেষ ক’টি বছর আল্লাহ্ তাওফীক দিয়েছিলেন আব্বার সঙ্গে ই‘তিকাফ করার। আল্লাহ্র ঘরে ই’তিকাফের সময় আব্বার সঙ্গে অন্যরকম একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। অনেক সময় আব্বার নিজের অতীত মেলে ধরতেন আমার কাছে। তখন মনে হতো, জীবনের কিছু একান্ত সম্পদ যেন বড় সন্তানের কাছে তিনি গচ্ছিত রাখছেন! যদি কখনো সুযোগ হয়...!
সম্ভবত সেবারই ছিলো আব্বার সঙ্গে আমার শেষ ই‘তিকাফ। অনেক কথার মধ্যে তিনি বলেছিলেন, তোমার আম্মা আমার জীবনে আল্লাহ্র অনেক বড় নেয়ামতরূপে ...!
.... তোমার দাদার দেয়া একটা মাত্র গলার হার ছিলো তোমার আম্মার। সেই হার আমার হাতে দিছিলো, পরের চাকরী বাদ দিয়া ছোট খাটো ব্যবসার করার জন্য।
আমি বললাম, তুমি আমার জন্য এত বড় কোরবানি করছো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?
তোমার আম্মার বলছিলো, এখনো যেন আমার কানে বাজে! কতটুকু বয়স আর ছিলো! তুমি তখনো দুনিয়াতে আস নাই। তোমার আম্মার বলছিলো, ‘আমার কিছু লাগবো না, খালি আমার আম্মার দিকে, আর এতীম ভাই-বোন গুলার দিকে খেয়াল রাইখেন।...
তোমার আম্মার সেদিনের সেই কথা সারা জীবন আমি পালন করার চেষ্টা করছি।...
এই ছিলেন তখনকার তিনভাই-বোনের বালিকাবয়সের বড় আপা, আজ বার্ধক্যে প্রায় অচল হয়ে পড়া আমার আম্মা, যিনি বহু দিন হলো স্বামীর রক্ষাছায়া হারিয়েছেন, আর এই সেদিন হারিয়েছেন মায়ের ‘আঁচল’!
রামাযান শেষে ঈদের চাঁদরাতে বড় খালাম্মা যা বলেছিলেন, আসলে সত্যের দাবী রক্ষা করে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আকুতি থেকেই বলেছিলেন। জীবনের বড় দুর্বলতা এই যে, সত্যের দাবী ও কৃতজ্ঞতার আকুতি, এটা সবাই রক্ষা করতে পারে না এবং সবসময় পারে না। জীবনের ধূলোবালি জীবনের অনেক সত্যের অবয়ব মুছে ফেলতে চায় এবং মুছে ফেলে। মানুষ এমনই দুর্বল এবং অসহায় তার ভিতরের ‘অপসত্তা’র কাছে।
নানীর বড় নাতী, আর মায়ের প্রথম সন্তান হিসাবে আমি যা দেখেছি, যা এখনো আমার স্মৃতিতে প্রোজ্জ্বল, তাতে আমি বলতে পারি স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে, ঐ বয়সে নিজের সব সাধ-ইচ্ছা ভুলে গিয়ে আম্মা তাঁর মায়ের পাশে থেকে ভাইবোনদের জন্য মায়ের ভূমিকাই পালন করেছেন। হয়ত এ কথা কোন জিহ্বা এখন আর উচ্চারণ করবে না এবং কোন কান এখন আর শোনতে প্রস্তুত হবে না! তবে আমার বিশ্বাস আম্মার আমলনামায় নূরের হরফে তা লেখা থাকবে এবং হাশরের মাঠে নূরের পাল্লায় তার ওজন হবে, ইনশাআল্লাহ্।
***
নানার রেখে যাওয়া কিছু বই ছিলো, আর ছিলো কিছু জমির সামান্য কিছু আয়। তাতে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হওয়াই কঠিন, তা থেকে কিছু বাঁচিয়ে সঞ্চয় করা, এটা তো চিন্তা করাও ছিলো কঠিন। কিন্তু কঠিন কাজটি আব্বা নিজের সীনা-পসীনা এক করে সম্ভব করে তুলেছিলেন। কারণ দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিন থেকেই আব্বা এই এতীম পরিবারটির হাল ধরেছিলেন, নিজের দুর্বল হাতে, তবে জীবনের ব্রতরূপে।
আব্বা অনেক দিক চিন্তা করে বড় খালাম্মার বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন দাদার বাড়ীর একেবারে পাশে। যিনি আমার খালু হলেন তিনি আব্বার নিকটাত্মীয়। সেই বিবাহের কথা আমার মনে আছে। এখন বুঝতে পারি, বড় খালাম্মার সুখশান্তির কথা চিন্তা করে ঐ কঠিন সময়ে আব্বা কতটা উদার হাতে সব আয়োজন করেছিলেন। এমনকি পরবর্তী জীবনেও কিছু কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখে আব্বা কত কঠিন সংযমের সঙ্গে কত মনোরোঞ্জনমূলক আচরণ করেছিলেন, শুধু এ জন্য যে, খালাম্মা যেন শান্তিতে না হোক একটু স্বস্তিতে থাকতে পারেন। কিন্তু ...!
আমার মনে আছে, রাত বেশ গভীর হয়ে গিয়েছিলো খালাম্মাকে নিয়ে বরযাত্রীরা যখন বাড়ীতে আসে। এসেই ক্লান্ত শ্রান্ত বড় খালাম্মা ঘুমের কোলে ঢুলে পড়েছিলেন বলে...!
এটাও মনে আছে, একবার আম্মা ও খালাম্মা একসঙ্গে নানীর বাড়ীতে এসেছিলেন। নানী মুরগী রান্না করেছিলেন। আমি তো খুব খুশী! খেলামও বেশ আনন্দ করে। কত হবে তখন বয়স, পাঁচ কিংবা...! রাতে কিন্তু আমার সব আনন্দ বিষণতায় বদলে গেলো। বাতি নিভিয়ে সবাই শুয়ে পড়েছে, হঠাৎ শুনি আম্মা বড় খালাম্মাকে বলছেন, ‘আম্মায় তো আমগোরে মুরগী রাইন্দা খাওয়াইলো, কিন্তু আম্মায় যে এই কয়দিন কী কষ্ট কইরা চলছে! খাইয়া না খাইয়া আমগো লাইগা...। মনে হইলে গলা দিয়া কিছু নামতে চায় না। ...
আম্মা ভেবেছিলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। ঐ অবুঝ বয়সেও আম্মার কথা শুনে আমার এত কষ্ট হলো যে, কান্নাই পেয়ে গেলো। আম্মা তখন অস্থির হয়ে শুধু জানতে চান, ‘কী হইছে আবু! কী হইছে আবু!!’
সময়টা ঠিক মনে নেই। হয়ত আরো পরের ঘটনা। মনে আছে স্পষ্ট, নানী আব্দুল কাদের নানার ঘরে গিয়েছেন একটু শুঁটকি চেয়ে আনতে। মা-খালাদের জন্য শুঁটকির ভর্তা করবেন। এছাড়া আর কোন ব্যবস্থা ছিলো না। এখন বুঝতে পারি, নিজের জন্য নানী কিছুতেই যেতেন না, কিন্তু তাঁর মাতৃপ্রাণ সইতে পারেনি যে, মেয়েরা এসেছে মায়ের বাড়ীতে, অথচ ...!
যেভাবেই হোক বিষয়টা আম্মার জানা হয়ে গেলো। আম্মার চোখে তখন পানি আর ধরে না। শশুর বাড়ী যাওয়ার সময় আম্মার কাছে সামান্য যা ছিলো, জোর করে সেটা মায়ের হাতে দিয়েছিলেন। আর ভাইবোনদের রেখে চোখের পানিতে ভাসতে ভাসতে নৌকায় উঠেছিলেন। বর্ষাকাল ছিলো... সত্যি আমি বুঝতে পারি না, মায়ের কথা আগে বলবো, না মেয়ের কথা! বলতে ইচ্ছে হয়, আমার মা ধন্য, এমন মায়ের গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন; আমার নানী ধন্য যে, এমন মেয়ে তিনি গর্ভে ধারণ করেছেন।
‘অপরিপক্ব’ বয়স থেকে শুরু করে এই ‘পরিপক্ব’ বয়স পর্যন্ত, এমনকি নানীর মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত খুব নিকট থেকে নিজের চোখে যা দেখেছি, অবাক বিস্ময়ে, কিছুটা গর্বের সঙ্গে যা অনুভব করেছি তা এই যে, মেয়ে হয়েও এবং স্বামীর ঘরে থেকেও সারা জীবন আমার মা তার আম্মার জন্য পুত্রের কর্তব্যই পালন করেছেন, আর অনেকাংশেই তা সম্ভব হয়েছে আমার আব্বার মহানুভবতার কারণে। আমার অবর্তমানের কথা এবং অবুঝ বয়সের কথা তো আম্মার কাছে এবং বড় খালাম্মার কাছে কিছু শুনেছি। তবে বুঝ হওয়ার পর যা দেখেছি, এককথায় যে কোন মানুষের জন্য তা ছিলো অনুকরণযোগ্য। এটা ঠিক, আমার আব্বা সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন, ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না, তবে তিনি যা ছিলেন তার নমুনা তখনকার সময়েও প্রচুর ছিলো না। ...
আগেই বলেছি, কিছু বই ছাড়া নানার ঘরে নগদ কোন সঞ্চয় ছিলো না। ঐ বইগুলো আব্বা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে দিয়ে আসতেন। বইগুলো কিছুটা সময় নিয়ে হলেও ‘বিতরিত’ হয়ে যেতো, তবে সেখান থেকে অর্থ উদ্ধার করে আনা যে কী কঠিন ছিলো তা নিজের এখনকার অতি সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেও আন্দায করতে পারি। উর্দূতে বলে, জুয়ে শির লানে সে কম নেহীঁ, বাংলায় বলে, পিঁপড়ের মুখ থেকে চিনির দানা বের করে আনা। সে অসাধ্যটাই আব্বার সাধন করেছেন, নিজের কর্মক্ষেত্রের দায়দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে।
বই বিতরণের অর্থ এবং দেশের সামান্য জমি থেকে যে আয় হতো, আব্বা মাটি কামড়ে চেষ্টা করতেন সেটা ধরে রাখতে। একারণে নানীর বাড়ীতে রীতিমত একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেলো, কিন্তু আব্বা ছিলেন অনড়। তাঁর ছিলো একটাই চিন্তা, যে কোন মূল্যে এতীমের জন্য ‘ঢাকার বাড়ীতে’ একটা ঠিকানা করতে হবে। এ লক্ষ্যে শশুর বাড়ীর সবার মতামত উপেক্ষা করে তিনি যে সাহসী সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছিলেন তা হলো, ছোট খালা ও মামাকেসহ নানীকে তিনি ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন, যাতে নানীর সংসারের আলাদা কোন খরচ না থাকে। এটা যে ঐ সময়ের জন্য আব্বার পক্ষ হতে কত বড় কোরবানী ছিলো তা যাদের বোঝার কথা তাদের সবাই না বুঝলেও বড় খালাম্মা আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত নছীব করুন বুঝতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ‘বড় দুলাভাইয়ের’ প্রতি এজন্য তিনি কৃতজ্ঞ ছিলেন যে, তাঁর উছিলায় ঢকা শহরে সবার সঙ্গে তাঁর বিধবা মা ও এতীম ভাইয়েরও ঠিকানা হয়েছে।
অবশ্য মানুষের স্বীকার-অস্বীকার ও কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতায় কিছু আসে যায় না, আশা করি, আল্লাহ্র কাছে আমার বাবা তাঁর কর্মের আজর ও প্রতিদান পাবেন ইনশাআল্লাহ।
১৯৬৪-এর দিকে কামরাঙ্গীরচর আশরাফাবাদে যখন আব্বা, বড় খালু এবং আব্বারও মুরুব্বি (আব্বার ফুফাত ভাই, জনাব মরহূম মুনীরুল হক ছাহেব) সবাই মিলে যখন জমি খরিদ করার চেষ্টায় নামলেন তখন মাটি কামড়ে ধরে রাখা সেই অর্থ দিয়ে নানার এতীম ছেলেটির জন্য ... কিছু ‘মাটি’ খরিদ করা হলো!
হাঁ, এখানে আব্বা শরীয়াতের বিষয়টি খেয়াল করেননি। তিনি নানার বিধবা স্ত্রী, তিন মেয়ের কথা চিন্তা না করে শুধু এতীম ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেছেন, আর সে জন্য পরে যথেষ্ট বিড়ম্বনারও সম্মুখীন হয়েছেন।
সেই এতীম ছেলে যিনি তখন আমার চেয়ে তিন বছরের বড়, আর আমার বয়স আট কি নয়; পরবর্তী জীবনে বড় দুলাভাইয়ের প্রতি সেই এতীম ছেলেটির দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি নিজের মত করেই গড়ে উঠেছিলো। ঐ রকম সময়ে আব্বা দাদার একটা কথা প্রায় স্মরণ করতেন।
***
মায়ের সেবা ও সন্তুষ্টি সাধনের জন্য আম্মার যে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা অন্তত আমি বুঝের হওয়ার পর থেকে দেখেছি তার সত্যি কোন তুলনা নেই। নানী কয়েকবারই কঠিন অসুস্থতায় পড়েছেন। তখন আম্মাকে যেভাবে দেখেছি দিনরাত মায়ের সেবায় নিবেদিত, তার উদাহরণ আগের যুগে কিতাবের পাতায় পাওয়া যায় কিছু, তবে বর্তমানে জীবনের পাতায় কমই পাওয়া যায়। একবারের কথা মনে আছে, নানীর অসুস্থতার সময় সারা রাত জেগে আম্মা নানীর সেবা করেছেন। মাথায় পানি দিয়েছেন। তখন বিদ্যুৎ ছিলো না; তাই শুধু বোতাম টিপে বাতাস করার দায় সারা যেতো না! আম্মা হাতপাখা নিয়ে অবিচল ভাবে নানীর শিয়রে বসে বাতাস করেছেন। তখন তাঁর যেন কোন ক্লান্তি ছিলো না। আল্লাহ্ যেন আম্মাকে তাঁর সারা জীবনের মাতৃসেবার উত্তম বিনিময় দান করেন। মায়ের হক আদায়ে যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে আল্লাহ্ যেন দয়া করে মাফ করে দেন। মায়ের হক তো এমন যে, কোন সেবা ও খেদমত এবং ত্যাগ ও আত্মত্যাগ দ্বারাই দু’ফোঁটা দুধের হক আদায় হবে না। আল্লাহ্র পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো উম্মতকে বোঝানোর জন্য বলেছেন, মা-বাবার হক শুধু তখনই আদায় হতে পারে যদি সন্তান তাদেরকে গোলাম অবস্থায় গোলামির কঠিন যিন্দেগিতে আবদ্ধ দেখতে পায়, আর বিপুল মূল্য দিয়ে তাদের খরিদ করে আযাদ করে দেয়। আল্লাহ্ যেন আমাকে এবং আমার ভাই-বোনদেরও মাফ করে দেন মায়ের ও বাবার হক আদায়ে ক্ষেত্রে যত ত্রুটি হয়েছে এবং হচ্ছে, আমীন।
***
নানীর প্রতি আমাদেরও কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। মেয়ের সংসারে যতদিন ছিলেন এবং বহু বছরই ছিলেন কখনো বসে ছিলেন না। বসে থাকা তাঁর স্বভাবের মধ্যে ছিলোই না। মেয়ের যেন কিছুটা আরাম হয়, বিশেষ করে সন্তানদের লালন পালনে, নানী তাঁর সাধ্যের ভিতরে অনেক করেছেন। বিশেষ করে, প্রথম নাতী হিসাবে আমাকে তো কোলে পিঠে করে...। আমার জন্মই তো হয়েছে নানীর বাড়ীতে এবং শৈশবের প্রায় সবটুকু কেটেছে নানীর বাড়ীতে। নানীর বিষয়ে এবং নানীর সঙ্গে আমার অনেক স্মৃতি সংরক্ষিত আছে হৃদয়ের মণিকোঠায়। সব যদি বলতে যাই, অনেক দীর্ঘ হবে সে মধুর কথামালা। একটি বাক্যই শুধু বলতে পারি এ প্রসঙ্গে,
আমার এবং পরবর্তী সময়েও ভাই-বোনদের প্রতিপালনে নানীর ত্যাগ ও আত্মত্যাগ এবং নিঃস্বার্থ সেবা ছিলো এমন যে, মুখের শব্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তার অসম্মান হয়। আগেও বলেছি, এখনো বলছি, সামনেও বলবো, যতদিন বেঁচে থাকি ‘আল্লাহ্ যেন তাকে উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করেন, আমীন।’
নানীর মুখে হাসি দেখেছি সামান্য, চোখের পানি দেখেছি, অনেক। বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে একজন বিধবার মুখের হাসি হবে কম, চোখের পানি হবে বেশী, এটা অবশ্য স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়। এদিকে আমার দেখার পরিধিও সামান্য। সেই সামান্য পরিধিতে এত কম হাসি এবং এত বেশী চোখের পানি আমি কম বিধবা নারীরই দেখেছি। যদিও আমার মা এবং বাবা তাঁদের সাধ্যের ভিতরে সবকিছু করেছেন। এমন অবশ্য হয়েছে, কোন প্রয়োজনের সময়ও আব্বা নানীর অনুরোধেও নানীর জন্য নানীর জমানো অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, এদিকে নিজেরও সাধ্য ছিলো সীমিত। এ কারণে আব্বাকে অনেকে অনেক রকম বুঝেছে; এমনকি নানীও! তবে আব্বা ছিলেন তাঁর লক্ষ্যে অটল; ‘ঢাকার বাড়ীতে একটি ঠিকানা!’ আল্লাহ্র রহমতে, তারপর আব্বার সীমাহীন ত্যাগের কল্যাণে সেই ঠিকানা যখন হলো ঢাকার বাড়ীতে তখন ...!
তখন থেকে এখন, জীবনের দীর্ঘ পথ আমরা সবাই পাড়ি দিয়েছি। মাঝে মধ্যেই আমার একটা কথা মনে হয়েছে, সবফুলের যে সুবাস থাকে না, এটা বোধহয় প্রকৃতিরই দাবী। কারণ জীবন শুধু সুবাসেরই নাম নয়!
এখন তো নানীও কবরে, আব্বাও মাটির নীচে। আর নানা! তিনি তো পাড়ী দিয়েছেন সবার আগে। আশা করি বরযখের জগতে আল্লাহ্র রহমতে সবাই তাঁরা শান্তিতে আছেন, আমীন।
আগের কথাটা এখানে আবার বলতে হয়। কারণ মানুষ বারবার তার স্বভাবের কাছে পরাস্ত হয়। বারবার সে একই ভুল করে, নিজের জীবনের আলো, আর অন্যের জীবনের আঁধার বড় করে দেখে, পক্ষান্তরে নিজের জীবনের আঁধার, আর অন্যের জীবনের আলো এড়িয়ে যায়, দেখতেই যেন চায় না। শুধু এ কারণেই গীভর থেকে গভীর আমাদের সম্পর্কগুলোও এত ভঙ্গুর! রক্তের এবং আত্মার যে বন্ধনগুলো হওয়ার কথা চিরঅটুট সেগুলো পর্যন্ত কারণে অকারণে এবং তুচ্ছ কারণে হয়ে পড়ে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।
তো যে কথাটি এখানে আবার বলতে চাই তা এই যে, ভোরের আলো ও সন্ধ্যার আঁধার দু’টোই জীবনের সত্য। জীবনের সকল সম্পর্কের উপর, এমনকি মা ও সন্তানেরও স্পর্কের উপর ভোরের আলো যেমন প্রতিফলিত হয় তেমনি সন্ধ্যার আঁধারেরও ছায়াপাত ঘটে। কোন সম্পর্ক ও বন্ধন তখনই হয় অনুকরণীয় ও ঈর্ষণীয় যখন আলোর প্রখর প্রতিফলন আঁধারের ছায়া বারবার মুছে দেয়; মুছে দিতে পারে। আমার আম্মা ও তাঁর মায়ের জীবনেও আলো-আঁধারের উপস্থিতি ছিলো। তবে... আঁধারের ছায়া ছিলো এতই ক্ষীন ও ক্ষণস্থায়ী এবং আলোর বিকিরণ ছিলো এমনই প্রখর ও সর্বপ্লাবী যে, যারাই দেখেছে, অবাক হয়ে ভেবেছে, এমন মা এবং এমন মেয়ে এ যুগেও তাহলে হতে পারে! বিশেষ করে যখন ভাবি, নানী তাঁর মেয়ের সংসারে ছিলেন বছরের পর বছর এবং দীর্ঘকাল! তারপর সেখান থেকে গেলেন নিজের ঘরে, যেটা ছিলো মেয়ের বাড়ীর পাশে ঠিক লাগোয়া। যখন নানীর ‘বাড়ী’ হলো তখনো বহু দিন দেখেছি, দিন ও রাতের বেশীর ভাগ সময় হয় আম্মা নানীর কাছে, না হয় নানী তাঁর মেয়ের কাছে। এমনকি জীবনের শেষ দিকে এই সেদিনও, নানী যখন প্রায় চলতে পারেন না, আম্মা আরো কম চলতে পারেন, তবে নানী ছিলেন যথেষ্ট হালকা, নানীকে কোলে করে নিয়ে আসা হতো আম্মার কাছে। বসিয়ে দেয়া হতো মেয়ের পাশে। দেখে অবাক হতাম, ‘বুড়ির পাশে বুড্ডি’!! বিশেষ করে রামাযানে, আম্মা তেলাওয়াত করছেন, নানী তন্ময় হয়ে শুনছেন! ইচ্ছে হতো, বসে থাকি ‘আমার উপরের দু’টি সিঁড়ি’র পাশটিতে! ইচ্ছে হতো, তেলাওয়াত শুনি মায়ের গলার জান্নাতী সুরে, শুনতেই থাকি! বহুবার নানী বলেছেন, তোমার আম্মার কাছে বইলে তেলাওয়াত শুনলে পরানডা শান্তি হইয়া যায়!
এখানে এই সুযোগে বলতে ইচ্ছে করছে আমার আম্মার তেলাওয়াতের কথা, শৈশব থেকে শুনে এসেছি যে তেলাওয়াত; ঘুমিয়েছি যে তিলাওয়াত শুনে, জেগে উঠেছি যে তেলাওয়াত শুনে এবং...! এখন অবশ্য সৌভাগ্যের পরিধি খুব সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। মাঝে মধ্যেই শুধু শুনতে পাই, তাও ক্ষণিকের ‘পশলা’ বৃষ্টির মত। কারণ আমার মা যখন দিনে রাতে তাঁর ছোট্ট অঙ্গনে তিলাওয়াতে নিমগ্ন, আমি তখন আমার ‘অনেক বড় জগতটা’ নিয়ে ব্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত! হঠাৎ হঠাৎ যখন একপশলা বৃষ্টির মত মায়ের তিলাওয়াতের সান্নিধ্য গ্রহণ করি, সেই দূর শৈশবের কথা মনে পড়ে যায়! যখন আমার মনে হতো, আহা, এমন করুণ, বিগলিত সুরও আছে পৃথিবীতে!
নাহ, এখন বোধহয় থামতে হয়, এত কথা মায়ের হয়ত পছন্দ হবে না! একটা কথা বলেই থেমে যাই, আমি যখন তরুণ, আমার জীবনে যখন মা, আর মা; মা ছাড়া আর কেউ না, সেই তারুণ্যের সময় মনটা যখন কোন কারণে বিষণ হতো এবং হতো অস্থির ও বিক্ষিপ্ত, নামাযের পর মা তিলাওয়াত করতেন, আমি চুপটি করে মায়ের পাশে বসে থাকতাম! মায়ের তিলাওয়াত শুনে এবং শুনতে শুনতে মনের সব বিষণ তা, অস্থিরতা ও বিক্ষিপ্ততা ধুয়ের মুছে একেবারে পরিচ্ছন্ন হয়ে যেতো। মনটাকে তখন মনে হতো স্বচ্ছ আয়না, বা মেঘমুক্ত নীল আকাশ!
আরো পরে, যুবক বয়সে, এমনো হয়েছে, মনে কোন মন্দ চিন্তার কালো ছায়া পড়েছে; কথাগুলো বলছি এজন্য যে, এ যুগের মেয়েরা যেন বুঝতে পারে, সন্তানদের জন্য তাদের কেমন মা হতে হবে! তারা যেন বুঝতে পারে যে, শুধু মায়ের বিশুদ্ধ হৃদয়ের বিগলিত কণ্ঠের তিলাওয়াতের তাপ ও উত্তাপই সন্তানের জন্য হতে পারে কতটা রক্ষাকবচ!
হাঁ, মনে যখন কোন মন্দ চিন্তার কালো ছায়া পড়েছে, মন্দ হওয়ার ইচ্ছে তো কখনো ছিলো না, তাই মন্দের ঐ কালো ছায়া থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ভিতরে একটা অস্থিরতা তৈরী হতো! তখন সবার আগে যে কথাটা মনে হতো, ‘এখন আমাকে আম্মার কোরআন তিলাওয়াত শুনতে হবে!’
এত গুলো সন্তানের এমন ‘ভারী’ সংসারে আম্মা কীভাবে যেন তিলাওয়াতের সময় বের করে নিতেন! মায়ের তিলাওয়াত শুনতে পাওয়া তাই কঠিন ছিলো না। শুধু নিজের জন্য একটু অবসর তৈরী করে নিতে পারলেই হতো। মায়ের কাছে গিয়ে বসতাম, প্রায় সময় জায়নামাযেই পেতাম। তিলাওয়াত শুনতাম। মা ‘হয়ত’ জানতেন না, আমার ভিতরে তখন শুভ ও অশুভ-এর কী ভয়ঙ্কর দ্বন্দ্ব! আলো ও অন্ধকারের কী ভয়াবহ ঘাতপ্রতিঘাত! অন্ধকারের কালো থাবা থেকে উদ্ধার পেয়ে আলোর স্নিগ্ধতায় ফিরে আসার কী আকুতি!
আবারো বলছি, বিভিন্ন জালে মায়াজালে আটকা পড়ে খারাপ হয়ত আমি হতাম, কিন্তু কখনো খারাপ হতে চাইতাম না। ভালো হওয়ার এবং ভালো থাকার আকুতি ভিতরে সজীব ছিলো। আমি শুধু বলতে চাইছি, আমার জীবনে ভালো হওয়ার এবং ভালো থাকার বড় একটা অবলম্বন ছিলো আমার আম্মার কোরআন তিলাওয়াত।
তন্ময় হয়ে তিলাওয়াত শুনতাম। তখন মনে হতো, ভিতরের সেই কালো ছায়াটা ধীরে ধীরে যেন দূর হতে শুরু করেছে! ভোরের আলোর মত একটা কিছুতে আমার অন্তর যেন উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে!
বিশ্বাস করো ভাই, যখনই আমি আম্মার তিলাওয়াত শুনেছি, ভিতরে ভালো মানুষ হওয়ার একটা আকুতি অনুভব করেছি। আর এই আশা ও আশশ্বাস লাভ করেছি, ‘সম্ভব; আমার মায়ের সন্তান হিসাবে ভালো মানুষ হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব।’
হয়ত অপ্রাসঙ্গিক, তবু কলব থেকে কলমের মুখে একটা কথা এখানে ঝরে পড়তে চায়, আমার স্ত্রীর তিলাওয়াত, প্রথমে বলতে চেয়েছিলাম, ‘অনেকটা’, এখন সংশোধন করে বলছি, আমার স্ত্রীর তিলাওয়াত কিছুটা যেন আমার মায়ের তিলাওয়াতের মত। একই রকম মিহিন সুরে, প্রায় একই রকম বিগলিত কণ্ঠে। তবে তিনি তিলাওয়াত করেন কম এবং আমার শোনবার সুযোগ হয় আরো কম। তাঁর তিলাওয়াত শুনে তাঁর সন্তানের কী অনুভূতি হয়, জানি না, আমার মন শুধু সাক্ষ্য দেয়, এমন তিলাওয়াত যিনি করেন তাঁর উপস্থিতি কোন ঘর আলোকিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। (চলবে ইনশাআল্লাহ্)